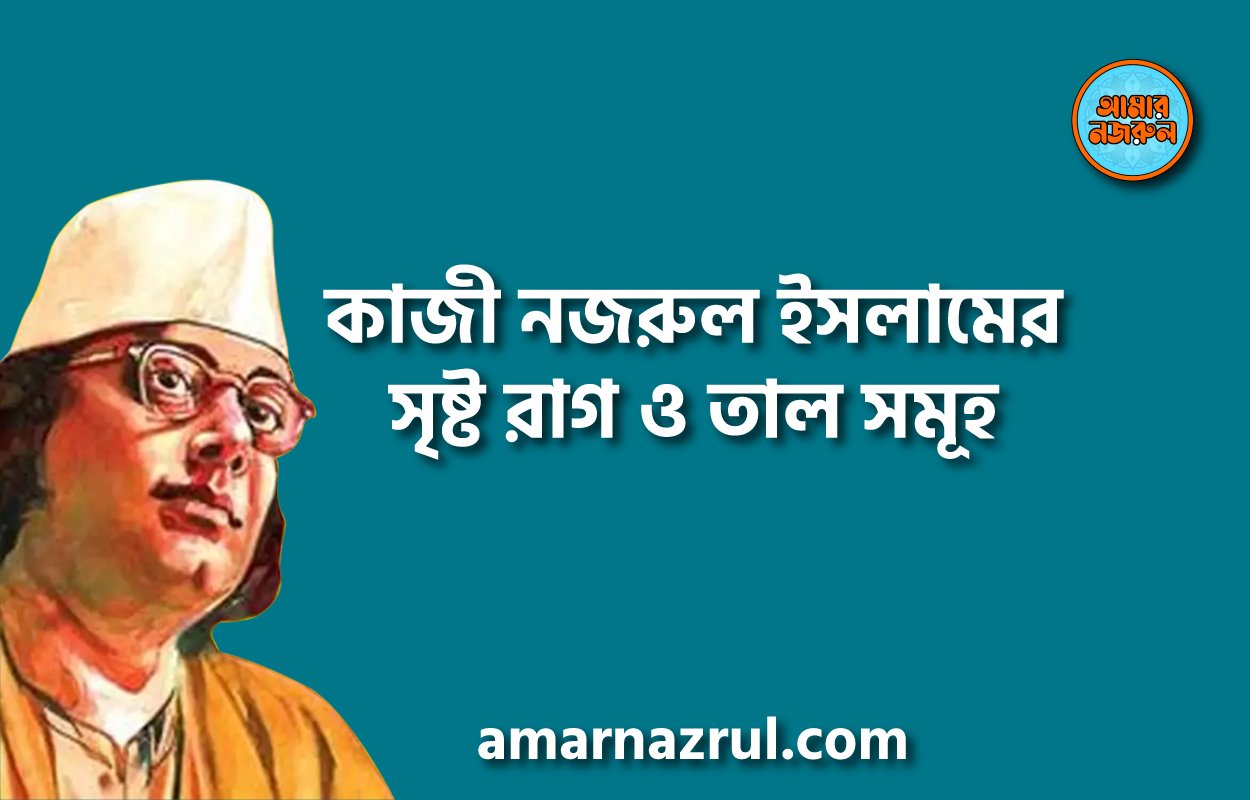কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্ট রাগ ও তাল সমূহ : কাজী নজরুল তার জীবদ্দশায় প্রচুর প্রচলিত ও অপ্রচলিত হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগে গান বেঁধেছেন। পাশাপাশি তিনি নতুন কিছু রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই রাগগুলো অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আজ জানবো সেসব রাগের আরোহ, আবরোহ, সহ কারিগরি বিষয়গুলো। তাছাড়া নজরুল কিছু তাল নিয়েও কাজ করেছিলেন। সেগুলো সম্পর্কেও জানবো।
কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্ট রাগ ও তাল সমূহ
রাগ-অরুণ ভৈরব :
রাগ অরুণ ভৈরব কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্ট একটি স্বতন্ত্র রাগ, যা তাঁর সঙ্গীতচর্চার এক অনন্য উদাহরণ। এই রাগটি ১৯৩৯ সালে রচিত ‘উদাসী ভৈরব’ নাটিকায় ব্যবহৃত হয়েছিল, যেখানে শিবের ধ্যানভঙ্গের প্রেক্ষাপটে গান পরিবেশিত হয়।
রাগ অরুণ ভৈরবের স্বরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য
- আরোহণ: ধা ণা সা ঝা সা গা মা, দা পা, ণা ধা সা
- অবরোহণ: সা ণা ধা ণা পা মা দা পা মা গা মা ঝা সা
- জাতি: বক্রসম্পূর্ণ
- বাদী স্বর: মধ্যম (মা)
- সমবাদী স্বর: ষড়জ (সা)
- বিশেষ স্বর: রে ও নি কোমল; ধা কখনো শুদ্ধ, কখনো কোমল রূপে ব্যবহৃত
- তাল: ঝাঁপতাল
- গ্রহস্বর: কোমল ধৈবত
এই রাগের সুরের গতি বজ্রগতির মতো, যা ধ্রুপদের গম্ভীরতা ও প্রশান্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। রাগটির স্নিগ্ধতা ও গভীরতা শ্রোতাকে ধ্যানমগ্নতার অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সাংগীতিক প্রয়োগ
‘উদাসী ভৈরব’ নাটিকায় শিবের ধ্যানভঙ্গের প্রেক্ষাপটে ‘জাগো অরুণ ভৈরব জাগো হে, শিবধ্যানী’ গানটি পরিবেশিত হয়। এই গানটি শিবের ধ্যানভঙ্গের প্রাথমিক পর্যায়ে সতী দ্বারা গীত, যেখানে শিবকে ‘অরুণ-ভৈরব’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নামকরণে শিবের তেজস্বিতা ও সূর্যের মতো দীপ্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে। গানটির সুরাঙ্গ ‘সাদরা’, যা ধ্রুপদের মতো গম্ভীর ও প্রশান্ত। নজরুল এই রাগে রচনা করেছেন ‘জাগো অরুণ ভৈরব জাগো হে, শিবধ্যানী’ গানটি, যা শিবের ধ্যানভঙ্গের প্রেক্ষাপটে পরিবেশিত হয়।
নজরুলের রাগসৃষ্টি ও সাংগীতিক অবদান
নজরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গীতচর্চায় নতুন রাগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা সঙ্গীতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। তিনি ‘অরুণ-ভৈরব’, ‘আশা-ভৈরবী’, ‘রুদ্র-ভৈরব’, ‘যোগিনী’, ‘শিবানী-ভৈরবী’ ও ‘উদাসী-ভৈরব’ সহ ছয়টি নতুন রাগ সৃষ্টি করেন।
শ্রবণ ও অনুশীলনের জন্য সম্পদ
রাগ অরুণ ভৈরবের সুর ও গানের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ছায়ানটের প্রকাশিত ‘জাগো অরুণ ভৈরব’ অডিও সিডি শোনা যেতে পারে, যেখানে এই রাগে গীত গানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই রাগের অনুশীলনের জন্য ইউটিউবে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল পাওয়া যায়, যা রাগ ভৈরবের আলাপ, স্বরমালিকা ও তান শেখার জন্য সহায়ক।
রাগ অরুণ ভৈরব নজরুলের সঙ্গীতসাধনার এক অনন্য নিদর্শন, যা তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও সঙ্গীতজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। এই রাগের মাধ্যমে তিনি বাংলা সঙ্গীতে নতুন রাগসৃষ্টির ধারা প্রবর্তন করেন, যা আজও সঙ্গীতপ্রেমীদের অনুপ্রেরণা জোগায়।
রাগ-রুদ্র ভৈরব :
রাগ রুদ্র ভৈরব হল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি প্রাচীন, গম্ভীর এবং শক্তিশালী রাগ, যা ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত। এই রাগটি ভোরবেলা পরিবেশনের জন্য উপযুক্ত, যখন প্রকৃতি গভীর শান্তি এবং ব্রহ্মমুহূর্তের পবিত্রতায় আচ্ছন্ন থাকে। এই রাগের সুরে মিশে থাকে প্রচণ্ড শক্তি, গভীরতা, এবং অপ্রতিরোধ্য ক্রোধের আবহ, যা মূলত শিবের রুদ্র রূপের সঙ্গে যুক্ত। শিবকে “রুদ্র” বলা হয়, যার অর্থ “প্রলয়ঙ্কর” বা ধ্বংসের প্রতীক। এই রাগের প্রতিটি সুরে সেই ভয়ংকর শক্তি ও আবেগ ফুটে ওঠে।
আরোহ: সা ঝা মা দা, ণা র্সা।
অবরোহ: সা ণা দা মা ঝ সা।
জাতি: ঔড়ব (পাঁচ স্বর ব্যবহৃত হয়)।
ঠাট: ভৈরব
বাদী স্বর: ধৈবত (ধা)
সমবাদী স্বর: ঋষভ (রে)
বাণী: প্রলয়ঙ্কর, শক্তিশালী, ক্রোধময়
স্বর বিন্যাস:
- কোমল স্বর: রে (ঋষভ), ধা (ধৈবত), নি (নিষাদ)।
- শুদ্ধ স্বর: সা (ষড়জ), মা (মধ্যম), পা (পঞ্চম)।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য:
- রাগটি উত্তরাঙ্গপ্রধান, অর্থাৎ এর মূল সুরভঙ্গি মধ্যম থেকে তার সা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- কোমল ঋষভ, ধৈবত, এবং নিষাদ স্বরের ব্যবহার রাগটিকে এক গভীর, শক্তিশালী আবহ দেয়।
- ধা এবং রে স্বরের মাঝে রাগটির শক্তির অভিব্যক্তি সবচেয়ে তীব্র।
- রাগটির মূল ভাব শক্তি, ক্রোধ এবং ধ্বংসের প্রতীক; তাই এটি মূলত তাণ্ডব নৃত্যের আবহ ধারণ করে।
প্রচলিত গান:
- “এস শঙ্কর ক্রোধাগ্নি, হে প্রলয়ঙ্কর রুদ্রভৈরব সৃষ্টি সংহর।”
- অনেক ধ্রুপদ, খেয়াল এবং উপশাস্ত্রীয় সঙ্গীতে এই রাগের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
ইতিহাস এবং প্রাচীন উল্লেখ:
- “নাট্যশাস্ত্র” এবং “সংগীত রত্নাকর” এর মতো প্রাচীন গ্রন্থে রাগ রুদ্র ভৈরবের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- বলা হয়, এই রাগটি আদিতে শুধুমাত্র যজ্ঞ এবং শক্তির উপাসনায় ব্যবহৃত হত।
- এটি প্রাচীনকালে যুদ্ধের আগে সৈন্যদের মধ্যে সাহস ও শক্তি সঞ্চার করার জন্য গাওয়া হত।
সমসাময়িক ব্যবহার:
- আধুনিক সঙ্গীত পরিচালকরা অনেক সময় এই রাগের স্বর ব্যবহার করে শক্তিশালী আবহ সঙ্গীত তৈরি করেন।
- অনেক চলচ্চিত্র, থিয়েটার এবং ডকুমেন্টারিতে এই রাগের শক্তিশালী প্রভাব দেখা যায়।
- ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি, এটি অনেক ফিউশন মিউজিক এবং রক সঙ্গীতেও ব্যবহৃত হয়েছে।
রাগ রুদ্র ভৈরব তার শক্তি, গভীরতা এবং ভয়ংকর আবহের কারণে আজও সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এটি শুধুমাত্র একটি রাগ নয়, বরং শক্তির উৎস এবং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক।
রাগ-আশা ভৈরবী :
রাগ-আশা ভৈরবী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি বিখ্যাত প্রভাতকালীন রাগ। এটি ভৈরব ঠাটের অন্তর্ভুক্ত এবং এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর কোমল স্বর, যা সঙ্গীতে এক গভীর, মিষ্টি এবং ভাবময় আবহ তৈরি করে। এই রাগ সাধারণত ভক্তিমূলক, ধ্যানমূলক এবং আত্মমগ্ন সঙ্গীতের জন্য উপযুক্ত।
📜 রাগের বৈশিষ্ট্য
- ঠাট: ভৈরব
- জাতি: সম্পূর্ণ-ঔড়ব (আরোহে সাতটি স্বর, অবরোহে পাঁচটি)
- আরোহ: সা – রে – গা – মা – পা – ধা – নি – সা
- অবরোহ: সা – ধা – পা – মা – গা – সা
- বাদী স্বর: পঞ্চম (পা)
- সমবাদী স্বর: ষড়জ (সা)
- কোমল স্বর: রে, গা, ধা, নি
- শুদ্ধ স্বর: মা, পা
- সময়: প্রভাত (সকালের প্রথম প্রহর)
🌅 মুড এবং আবহ
রাগ-আশা ভৈরবী সাধারণত একটি গম্ভীর, মায়াময় এবং ধ্যানমগ্ন আবহ তৈরি করে। এটি শুনলে প্রাকৃতিক প্রভাতের প্রশান্তি, একটি নতুন দিনের সূচনা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ অনুভব করা যায়। ভক্তিমূলক পরিবেশনার জন্য এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।
🎻 রাগের ব্যবহার এবং পরিবেশনা
রাগ-আশা ভৈরবী মূলত ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি এবং ভজনের মতো বিভিন্ন ধরণের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। এটি সেতার, সরোদ, বাঁশি, এবং সরস্বতী বীণার মতো তারবাহিত বাদ্যযন্ত্রেও সমানভাবে জনপ্রিয়। পন্ডিত রবিশঙ্কর, উস্তাদ বিলায়েত খাঁ এবং অনুষ্কা শঙ্করের পরিবেশনায় এই রাগ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।
🎵 উল্লেখযোগ্য গান এবং বাদ্য পরিবেশনা
- পন্ডিত রবিশঙ্করের সেতারে পরিবেশিত ‘রাগ আশা ভৈরব’।
- ভজন: ‘মেরা মন লাগা শ্যামরঙ্গী’
- ঠুমরি: ‘পিয়া বিন নাহি আয় চ্যাঁন’
রাগ-আশা ভৈরবী শুধুমাত্র সঙ্গীতের একটি রাগ নয়, এটি একটি অনুভূতি, এক আত্মবিশ্লেষণ এবং ভক্তির গভীরতায় নিমগ্ন হওয়ার এক সঙ্গীতীয় পথ। এটি ভারতীয় সঙ্গীতের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য যা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে সুর মেলাতে সাহায্য করে।
রাগ-শিবানী-ভৈরবী :
রাগ শিবানী ভৈরবী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এক অপূর্ব ও হৃদয়স্পর্শী রাগ। এই রাগটি ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত এবং এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো গভীর ভক্তি ও শিবানী (পার্বতী) দেবীর প্রতি নিবেদিত অনুভূতির প্রকাশ। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু ধর্মে দেবী পার্বতীকে ‘শিবানী’ বলা হয়, যিনি দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গিনী। তাই, এই রাগের মধ্যে মহাদেব ও শিবানীর ভক্তির মিশ্রণ প্রতিফলিত হয়।
🎵 রাগের মৌলিক বৈশিষ্ট্য:
- ঠাট: ভৈরব
- জাতি: ঔড়ব-সম্পূর্ণ (আরোহে পাঁচটি স্বর, অবরোহে সাতটি)
- আরোহ: সা – রে – গা – পা – ধা – সা
- অবরোহ: সা – নি – ধা – পা – মা – গা – রে – সা
- বাদী স্বর: ষড়জ (সা)
- সমবাদী স্বর: পঞ্চম (পা)
- কোমল স্বর: গা, ধা, নি
- শুদ্ধ স্বর: রে, মা, পা
- সময়: ভোর বা প্রভাতকাল
- ভাব: ভক্তি, শান্তি ও আধ্যাত্মিকতা
🎶 রাগের সুরের গঠন ও ব্যবহার:
শিবানী ভৈরবীর সুরের গঠন গভীর ও মৃদু। এর কোমল গা, ধা, নি স্বরগুলির ব্যবহার একটি কোমল অথচ গম্ভীর আবহ সৃষ্টি করে, যা ভোরবেলার পরিবেশের সাথে মিলে যায়। রাগটি মূলত ভক্তিমূলক গান ও ধ্যানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং প্রভাতের সময় পরিবেশন করা হয়, যখন প্রকৃতি শান্ত ও পবিত্র থাকে।
🌸 রাগের আধ্যাত্মিকতা:
শিবানী ভৈরবী শুধু একটি সুর নয়, এটি আধ্যাত্মিকতার এক গভীর প্রকাশ। এটি শ্রোতাকে মহাদেব ও শিবানীর অনন্ত প্রেম ও ঐশ্বরিক শক্তির অনুভূতিতে নিয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরে এই রাগের মাধ্যমে দেব-দেবীর প্রতি ভক্তির নিবেদন করা হতো।
🎤 বিখ্যাত পরিবেশনাগুলি:
পন্ডিত রবি শঙ্কর, উস্তাদ বিলায়েত খান এবং বহু প্রথিতযশা শিল্পী এই রাগে তাঁদের পরিবেশনায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। এই রাগে পরিবেশিত কিছু জনপ্রিয় গান হল:
- ‘ভগবান শিব জাগো জাগো’
- ‘শিবানী শিবানী মা জাগো’
রাগ শিবানী ভৈরবী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এক অনন্য সৃষ্টি, যা শ্রোতাদের আধ্যাত্মিক ও ভক্তিমূলক অনুভূতিতে নিয়ে যায়। এর প্রতিটি স্বরে যেন এক মহাশক্তির স্পর্শ লুকিয়ে আছে।
রাগ-রক্তহংস সারং:
রাগ-রক্তহংস সারং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক বিশেষ রাগ, যা তার সুরের গভীরতা এবং আবেগময়তার জন্য পরিচিত। এটি মূলত হিন্দুস্তানি সঙ্গীত ঘরানার একটি আধুনিক সৃষ্টি, যা প্রাচীন রাগ সারং-এর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। রাগটি তার মিষ্টি সুর ও সৌন্দর্যের জন্য বিশেষভাবে জনপ্রিয়।
আরোহ ও অবরোহ:
রাগ-রক্তহংস সারং-এর গঠন ঔড়ব-ঔড়ব, অর্থাৎ এতে আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্ষেত্রেই পাঁচটি করে স্বর ব্যবহৃত হয়।
- আরোহ (উর্ধ্বগমন): সা রে মা পা ধা সা
- অবরোহ (নিম্নগমন): সা ধা পা মা রে সা
প্রধান ও সহ-প্রধান স্বর:
এই রাগের বাদী (প্রধান) স্বর হল পঞ্চম (পা), যা রাগটির মূল শক্তি প্রদান করে। এর সমবাদী (সহ-প্রধান) স্বর হল ঋষভ (রে), যা রাগটির অভিব্যক্তিকে আরও সমৃদ্ধ করে।
স্বর প্রকৃতি:
রাগ-রক্তহংস সারং-এর বিশেষত্ব হল এর সকল স্বর শুদ্ধ, যা রাগটির সুরকে অত্যন্ত পরিষ্কার ও নির্মল করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্য রাগটিকে একটি শীতল, শান্ত এবং মানসিক প্রশান্তির অনুভূতি প্রদান করে।
রাগটির বৈশিষ্ট্য:
রক্তহংস সারং একটি সন্ধ্যা কালের রাগ, যা সাধারণত দিনের শেষ ভাগে পরিবেশিত হয়। এটি এক ধরনের গভীরতা ও আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি করে, যা মনকে একটি শান্ত, নির্ভার অবস্থায় পৌঁছে দেয়।
প্রচলিত গান ও রচনাঃ রাগ-রক্তহংস সারং-এ কিছু উল্লেখযোগ্য গান রচিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো:
“বল রাঙা হংসদূতী, তার বারতা দাও তার বিরহ-লিপি, বল সে কোথা।”
এই গানটি রাগটির আবেগময়তা ও সুরের মাধুর্যকে তুলে ধরে। এর সুরে একধরনের অন্তর্নিহিত ভালোবাসা ও বিরহের অনুভূতি ফুটে ওঠে।
উপসংহার: রাগ-রক্তহংস সারং তার সরলতা, সুরের মাধুর্য এবং আবেগময়তার জন্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এটি সঙ্গীতপ্রেমীদের হৃদয়ে একটি গভীর প্রভাব ফেলে এবং শ্রোতাদের মনকে একধরনের আত্মিক প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয়।
রাগ-সন্ধ্যামালতী:
রাগ সন্ধ্যামালতী বাংলা সংগীতের জগতে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি, যা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সুরসাধনার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই রাগটি ১৯৪০ সালের ১৩ জানুয়ারি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত ‘নব রাগমালিকা’ গীতিনাট্যের প্রথম পর্বে প্রথমবারের মতো পরিবেশিত হয়েছিল ।
রাগ সন্ধ্যামালতীর সংগীততত্ত্ব
স্বরবিন্যাস
- আরোহ: সা, রে, গা, মা, পা, গা, ধা, মা, পা, না, রে, সা
- অবরোহ: সা, না, ধা, পা, মা, গা, রে, সা
স্বরপ্রয়োগ
- জাতি: বক্র সম্পূর্ণ
- বাদী স্বর: পঞ্চম (পা)
- সমবাদী স্বর: ষড়জ (সা)
- বিশেষ স্বরপ্রয়োগ:
- গা, ধা, এবং না — কোমল ও শুদ্ধরূপে
- মা — তীব্র
এই রাগে স্বরগুলির বক্র ব্যবহারে এক অনন্য সুরের আবহ সৃষ্টি হয়, যা শ্রোতাকে সন্ধ্যার নরম আলো ও প্রশান্তির অনুভূতি প্রদান করে।
রাগের নামকরণ ও প্রাকৃতিক অনুপ্রেরণা
‘সন্ধ্যামালতী’ নামটি একটি বিশেষ ফুলের নাম থেকে আগত, যার বৈজ্ঞানিক নাম Mirabilis jalapa এবং ইংরেজিতে ‘Four o’clock flower’ নামে পরিচিত। এই ফুলটি বিকেলের দিকে ফোটে এবং পরদিন সকালে ম্লান হয়ে যায় । নজরুল এই ফুলের সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্য ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখে রাগটির নামকরণ করেছেন।
রাগের আবহ ও অনুভূতি
রাগ সন্ধ্যামালতী মূলত সন্ধ্যাকালীন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর সুরে সন্ধ্যার নরম আলো, প্রশান্তি এবং এক ধরনের বিষণ্ণতা প্রকাশ পায়। এই রাগে গাওয়া গান ‘সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী বেলা শেষের বাঁশী বাজে’ এই আবহকে আরও গভীরভাবে তুলে ধরে।
নজরুলের সঙ্গীতে রাগের গুরুত্ব
কাজী নজরুল ইসলাম ভারতীয় ঠাট-রাগ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং নতুন রাগ সৃষ্টিতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিলুপ্তপ্রায় রাগগুলিকে নতুন সঙ্গীত সৃষ্টি করে নবজীবন দান করেছেন । রাগ সন্ধ্যামালতী তাঁর এই সৃজনশীলতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।
রাগ সন্ধ্যামালতী বাংলা সংগীতের জগতে নজরুলের এক অনন্য সৃষ্টি, যা তাঁর সুরসাধনার গভীরতা ও সৃজনশীলতার প্রতিফলন। এই রাগের মাধ্যমে তিনি সন্ধ্যাকালীন প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবমনের অনুভূতিকে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, যা আজও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।
রাগ-বনকুন্তলা :
রাগ বনকুন্তলা একটি স্বতন্ত্র ও মনোমুগ্ধকর রাগ, যা হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীতের জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এর সুর ও চলন একদিকে যেমন প্রকৃতির কোমলতা প্রকাশ করে, তেমনি অন্যদিকে এক গভীর আবেগের সঞ্চার ঘটায়।
রাগের পরিচিতি
- আরোহ (উর্ধ্বগমন): পা ধা সা রে গা পা ধা পা ধা না
- অবরোহ (নিম্নগমন): সা না ধা পা গা রে গা সা
- জাতি: ঔড়ব-যাড়ব (আরোহে পাঁচটি স্বর, অবরোহে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত)
- বাদী স্বর: পঞ্চম (পা)
- সমবাদী স্বর: ষড়জ (সা)
- থাট: কাফি থাটের অন্তর্ভুক্ত
- সময়: সন্ধ্যা বা রাতের প্রথম প্রহর
রাগের বৈশিষ্ট্য
রাগ বনকুন্তলা তার সুরের মাধ্যমে একটি কোমল ও মায়াবী আবহ সৃষ্টি করে। এর আরোহ ও অবরোহে ব্যবহৃত স্বরসমূহের বিন্যাসে একটি স্বপ্নময় অনুভূতি জাগ্রত হয়। পঞ্চম (পা) এর উপর ভিত্তি করে রাগটি গঠিত, যা রাগের মূল আবেগকে ধারণ করে।
রাগের অনুভূতি ও প্রভাব
বনকুন্তলা রাগের সুরে একটি শান্ত, কোমল ও মায়াবী আবহ সৃষ্টি হয়। এর সুরের মাধ্যমে শ্রোতার মনে একটি স্বপ্নময় অনুভূতি জাগ্রত হয়, যা প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবিক আবেগের মেলবন্ধন ঘটায়।
রাগ বনকুন্তলা হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি অনন্য রাগ, যা তার সুরের মাধ্যমে শ্রোতার মনে গভীর আবেগ ও অনুভূতির সৃষ্টি করে। এর সুরের মাধুর্য ও কোমলতা সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে।
রাগ-বেণুকা :
রাগ বেণুকা হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাগ, যা তার অনন্য স্বরবিন্যাস ও বজ্রগতির জন্য পরিচিত। এই রাগের গঠন, স্বরচরিত্র এবং প্রয়োগের দিক থেকে এটি সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের বিষয়।
রাগের গঠন ও স্বরবিন্যাস
- আরোহ (উর্ধ্বগমন): সা রে মা, পা ধা পা ধা মা পা ধা নি
- অবরোহ (নিম্নগমন): সা নি পা ধা নি, গা রে গা সা
- জাতি: ষাড়ব-ষাড়ব (ষড়জ ও পঞ্চম ব্যতীত ষড়ব স্বর)
- বাদী স্বর: মধ্যম (মা)
- সমবাদী স্বর: ষড়জ (সা)
এই রাগে আরোহ গতিতে কোমল নিশাদ (নি) ব্যবহার হয়, যা রাগটির আবেগময়তা ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করে। অন্য সব স্বর শুদ্ধ থাকে, যা রাগটির স্বচ্ছতা ও স্থিতি বজায় রাখে।
রাগের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ
রাগ বেণুকা বজ্রগতির রাগ হিসেবে পরিচিত, যার অর্থ এটি দ্রুত ও শক্তিশালী গতিতে পরিবেশিত হয়। এই রাগের সুরপ্রবাহ শ্রোতাদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। রাগটির গঠন এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে এটি দ্রুত গতির তান ও আলঙ্কারিকতা প্রদর্শনে উপযোগী।
রাগ বেণুকা সাধারণত দিনের প্রথমভাগে পরিবেশিত হয়, যখন প্রকৃতি নবজীবনের স্পন্দনে মুখরিত থাকে। এই রাগের মাধ্যমে সেই প্রাকৃতিক উচ্ছ্বাস ও প্রাণচাঞ্চল্য সংগীতে প্রতিফলিত হয়।
উল্লেখযোগ্য রচনাঃ “রেণুকা ও কে বাজায় মহুয়া বনে“
রাগ বেণুকার একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল “রেণুকা ও কে বাজায় মহুয়া বনে”। এই গানটি রাগটির সুরপ্রবাহ ও আবেগময়তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। গানটির মাধ্যমে রাগ বেণুকার গাম্ভীর্য ও উচ্ছ্বাস একত্রে প্রকাশ পায়, যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।
রাগ বেণুকা হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি অনন্য রাগ, যা তার স্বরবিন্যাস, গতি ও আবেগময়তার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এই রাগের মাধ্যমে সংগীতশিল্পীরা তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারেন। রাগ বেণুকা সংগীতপ্রেমীদের জন্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যা শ্রবণে এক গভীর তৃপ্তি এনে দেয়।
রাগ-উদাসী ভৈরব :
উদাসী ভৈরব বাংলা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্যতম গভীর ও প্রভাবশালী রাগ। এ রাগের সুর ও ছন্দে বিরাজমান থাকে এক বিশেষ ধরনের বিষাদ ও অন্তর্মুখী মনোভাব, যা শ্রোতাকে এক মায়াময় অনুভূতির জগতে প্রবেশ করায়। শাস্ত্রীয় রাগতত্ত্ব অনুযায়ী উদাসী ভৈরব রাগের সুরের উপাদান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:
স্বরলিপি ও রাগের গঠন
- আরোহ (উদয়): সা, ঝা, গা, মা, ক্ষমা, ক্ষণসা, বার্সা
- অবরোহ (অবনমনী): কাণাহ্মা, মা, মা, গা, ঝা, সা
- জাতি: বক্রগতির ঔড়ব-ঔড়ব
- বাদী স্বর (প্রধান নোট): মধ্যম (মা)
- সমবাদী স্বর (সহায়ক নোট): ষড়জ (সা)
এই রাগের বিশেষত্ব হলো এতে রে (ধ্রুপদী রাগের ঋষভ) এবং নিস্বর (পঞ্চম) স্বর দুটি কোমল (কম গামকসহিত) রূপে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি দুই প্রকার মধ্যম (তৎপর ও কোমল) স্বরও ব্যবহৃত হয়, যা রাগটিকে বিশেষ রকমের মাধুর্য ও গভীরতা প্রদান করে।
সাদৃশ্য ও বৈশিষ্ট্য
উদাসী ভৈরব রাগের সুরতত্ত্বে ললিত রাগের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ললিত যেমন কোমল ও বিষাদময়, তেমনি উদাসী ভৈরবও গভীর বিষাদের প্রকাশ ঘটায়। তবে উদাসী ভৈরবের সুরে একটা দার্শনিক ভাব ও অন্তর্মুখী মনোভাব স্পষ্ট, যা শ্রোতাকে একান্ত ভাবনায় নিমগ্ন করে।
এই রাগের গীতি, ভজন বা রাগিণীতে বিষাদের ছোঁয়া যেমন থাকে, তেমনি তা কখনো কখনো নিরাশা ও তীব্র অন্তর্দর্শনের অভিব্যক্তি বহন করে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত ও নাটকে উদাসী ভৈরবের ব্যবহার প্রায়শই এমন অনুভূতির জন্য হয়ে থাকে যা গভীর শোক বা বিষণ্নতা প্রকাশ করে।
সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উদাসী ভৈরব
বাংলা গানের জগতে উদাসী ভৈরব রাগটি বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুল গানে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে গভীর মেলানকোলিয়া ও দার্শনিক বিষাদের সুর সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, “গান-সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাদে/বিষাণ ত্রিশুল ফেলি”—এই পংক্তি রাগটির অন্তর্মুখী এবং শোকাকুল ভাবের প্রকাশ।
ভৈরব রাগ মূলত বিষাদের বিভিন্ন স্তরকে ফুটিয়ে তোলে, যা বিশেষ করে ধ্যান, অনুশোচনা ও দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে সুসংগত। এর মধ্যে ‘ভৈরব’ শব্দটি দেহ ও মনকে সজীব করার অগ্নিশক্তির প্রতীক হলেও, উদাসী ভৈরব এই শক্তিকে এক ধরণের নিরব ও গভীর বিষাদের আভায় উপস্থাপন করে।
উদাসী ভৈরব রাগ বাংলা সঙ্গীতের এক অনন্য রত্ন, যা তার বক্রগতির গঠন ও স্বর ব্যবহারে শ্রোতার হৃদয়ে এক গভীর ছাপ ফেলে। এটি শুধুমাত্র একটি সুর নয়, বরং এক ধরনের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ যা মানুষের মনের বিষাদের গভীরতম স্তরকে স্পর্শ করে।
শাস্ত্রীয় সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য উদাসী ভৈরব রাগ হলো একটি অনন্য অধ্যায়, যেখানে সঙ্গীত ও মনস্তত্ত্ব মিলেমিশে তৈরি করে এক অনন্য শোকসুরভিত অভিজ্ঞতা।
রাগ-শঙ্করী:
ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অপরিসীম ভান্ডারে রাগ শঙ্করী একটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী এবং সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশকারী রাগ। এটি শ্রোতাদের হৃদয়ে এক মাধুর্যময়ী অভিজ্ঞতা জন্মায়, যার মাধ্যমে প্রায়ই গভীর প্রেম, ভক্তি ও দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ পায়। শঙ্করী রাগের ইতিহাস, গঠন এবং এর বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করা হলো।
রাগের গঠন:
আরোহ:
সা গা পা না ধার্সা
(সংখ্যায়: ১ ৩ ৫ ৬ ৭)
অবরোহ:
সা না পা, গা পা গা পা, গা সা
(সংখ্যায়: ১ ৭ ৫, ৩ ৫ ৩ ৫, ৩ ১)
জাতি: ঔড়ব-ঔড়ব (পঞ্চম এবং সপ্তম সুরের কুঁটস্বরূপ বা ব্যবহারে আধুনিকীকরণ)
বাদী স্বর: গান্ধার (গা)
সমবাদী স্বর: নিষাদ (নি)
রাগের বৈশিষ্ট্য:
শঙ্করী রাগের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এর অবরোহে কোমল নিষাদের (নি) ব্যবহার, যা রাগটিকে অতিরিক্ত কোমল এবং মৃদু শৈলীতে উপস্থাপন করে। আরোহে স্বরগুলো প্রধানত শুদ্ধ থাকে, যা রাগের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং শ্রোতাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।
এই রাগের ব্যবহার অনেক সময় শিবের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভক্তির সঙ্গেও সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে, শঙ্করী নামটি হয়তো শিবশক্তির ঐক্যের প্রতীক। শিবানী বা অঙ্গলীনা যোগমায়া শঙ্করী এই রাগের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
শঙ্করী রাগের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব:
শঙ্করী রাগ বাঙালি কাব্য ও সংগীতের মধ্যেও ব্যাপক জনপ্রিয়। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী গান যেমন:
- বালিকা সমলীলাময়ী নীল উৎপল পাণি
এ ধরনের গানে এই রাগের ব্যবহার দেখা যায়, যেখানে প্রেমের সরলতা, কোমলতা ও মাধুর্য ফুটে ওঠে।
শঙ্করী রাগে শিবভক্তি এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের রসের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। এটি প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্মেষ এবং মানব আবেগের গভীরতা প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যম।ৱ
ব্যবহার ও প্রসঙ্গ:
শঙ্করী রাগের স্বরলিপি ও সুরের গঠন এটিকে মূলত সন্ধ্যা এবং গভীর রাতের রাগ হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি প্রায়ই ধীরগতির আলাপ বা বন্ধনীর (ভক্তিমূলক) গান এবং নজরুল গীতি বা বাউল গানে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিক শাস্ত্রেও শঙ্করীকে একটি আবেগঘন, গভীর ভাবের রাগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
রাগ শঙ্করী বাংলা এবং ভারতীয় সঙ্গীতের একটি নিখুঁত রূপক যেখানে মধুরতা, আধ্যাত্মিকতা এবং আবেগের সঙ্গম ঘটে। এর বিশেষ আরোহ-অবরোহ, বাদী ও সমবাদী স্বরের ব্যবহার, এবং কোমল নিষাদের স্বরবিন্যাস রাগটিকে অন্যান্য রাগ থেকে আলাদা করে দাঁড় করায়। প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত শঙ্করী রাগের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতপ্রেমীরা একটি অনন্য অনুভূতি অর্জন করে আসছেন যা সময়ের সাথে সাথে আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে।
রাগ-যোগিনী:
রাগ যোগিনী বাংলা ও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক স্বতন্ত্র ও মনোমুগ্ধকর রাগ। এটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বক্র সম্পূর্ণ জাতির অন্তর্গত এবং এর সুর ও ছন্দ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। রাগ যোগিনী গানের মাধ্যমে শিল্পী নানা আবেগের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হন—যা কখনো শান্ত, কখনো বিষণ্ণ, আবার কখনো প্রেম-বিরহের মিলন।
রাগের আরোহ এবং অবরোহ
রাগ যোগিনীর আরোহ (উপরের সুরগমন) হলো:
সা ঝা জ্ঞা হ্মা দা পা, মা পা ণা দা পা সা।
অর্থাৎ, রাগটি উচ্চ সুর থেকে শুরু হয়ে মধ্য ও নিম্ন সুরে নেমে আসে।
অপরদিকে, রাগের অবরোহ (নিম্ন থেকে উচ্চ সুরে গমন) হল:
সা না দা পা, পাহ্মাগা, মা, মাঝা সা।
এই সুরপথ রাগটিকে একটি বক্র ও সম্পূর্ণ জাতির স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়, যেখানে স্বরগুলো বিন্যাস ও নিয়মে পরস্পরের সাথে আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করে।
রাগের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
- জাতি: বক্র সম্পূর্ণ
- বাদী স্বর: পঞ্চম স্বর ‘পা’ (Pa)
- সমবাদী স্বর: ষড়জ বা মূল স্বর ‘সা’ (Sa)
- বিশেষত: এই রাগে ‘রে’ (Re) ও ‘ধ’ (Dha) স্বর দুটি কোমল (কম তীব্র) ধাঁচে ব্যবহৃত হয়। ‘মা’ (Ma) স্বর তীব্র এবং শুদ্ধ রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং ‘গ’ (Ga) ও ‘নি’ (Ni) স্বর কোমল ও শুদ্ধ রূপে ব্যবহৃত হয়। এই সংমিশ্রণে রাগের সুরগতিতে এক অনবদ্য কোমলতা ও মাধুর্য প্রকাশ পায়।
রাগের আবেগ ও ভাবগম্ভীরতা
রাগ যোগিনী সাধারণত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে শিল্পীরা বিরহ, বিষণ্ণতা, শান্তি এবং অন্তর্মুখী ভাবনা প্রকাশ করতে পারেন। রাগের বিশেষ সংগঠন এবং তার সুরের মাধুর্য শোনার পর মন যেন একশ্রেণী নীরবতার মাঝে প্রবেশ করে, যেখানে জীবনের সব কষ্ট আর ক্লেশ এক পলকে বিমূঢ় হয়ে যায়।
রাগ যোগিনীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে রাগের নামকরণ প্রায়ই দেবী-দেবতার বা পৌরাণিক চরিত্রের সাথে যুক্ত থাকে। “যোগিনী” শব্দের অর্থ হলো এক ধরনের আধ্যাত্মিক নারী শক্তি বা দেবী, যারা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই রাগ যোগিনী শব্দার্থে এমন এক সুরের প্রকাশ যেখানে মাধুর্য ও শক্তির এক অসাধারণ মিশ্রণ বিদ্যমান।
রাগ যোগিনী কেবল একটি সুরের সমষ্টি নয়, এটি একটি সম্পূর্ণ আবেগের ভাষা, যা শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে এক অনন্য সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। এর কোমল কিন্তু শক্তিশালী সুরের ছোঁয়া জীবনের নানা দুঃখ-বেদনা ও আনন্দের সাথে সঙ্গীতকে মেলবন্ধনে পরিণত করে। তাই রাগ যোগিনী আজও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক অমূল্য রত্ন হিসেবে বিবেচিত।
রাগ-শিব সরস্বতী :
রাগ শিব সরস্বতী হিন্দু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট রাগ, যার নামকরণ শিব ও সরস্বতী দেবীর প্রতি উৎসর্গীকৃত। এটি এক ধরনের ষাড়ব–ষাড়ব জাতির রাগ, অর্থাৎ তার aroha (আরোহ) ও avaroha (অবরোহ) উভয়েই ছয়টি স্বর নিয়ে গঠিত।
স্বরবিন্যাস
- আরোহ (আরোহণ):
দা – না – সা – গা – মা, দা – পা, জ্ঞা – মা – সা - অবরোহ (অবরোহণ):
সা – না – দা – মা, দা – পা – মা – জ্ঞা – মা – সা
এই রাগে বাদী স্বর (Dominant note) হচ্ছে মধ্যম (মা) এবং সমবাদী স্বর (Sub-dominant note) হলো ষড়জ (সা)। রাগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গ (গন্ধার) এবং ধ (ধৈবর্ত) স্বরের ব্যবহার, যা হয় কোমল (komal) অথবা শুদ্ধ (shuddha) উভয়ভাবেই ধরা হয়।
সুর ও ভাব
শিব সরস্বতী রাগের সুরময়তা এবং এর ঐশ্বরিক অনুভূতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি সাধারণত প্রাতঃকালীন বা সন্ধ্যাকালীন পরিবেশে ব্যবহার হয়, যেখানে রাগটি শ্রোতাদের মনকে প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিক গভীরতায় নিয়ে যায়। এই রাগে ব্যবহৃত কোমল স্বরগুলি শান্ত ও মৃদু আবেগ সঞ্চার করে, যা শ্রোতার মনের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করে।
রাগের বৈশিষ্ট্য
- গন্ধার (গ) এবং ধৈবর্ত (ধ) স্বরের ভুমিকা: এই রাগে গন্ধার স্বরটি কখনো কোমল এবং কখনো শুদ্ধভাবে ব্যবহার করা হয়, যা রাগের ভিন্ন ভিন্ন রঙ তুলে ধরে। ধৈবর্ত স্বরটিও প্রধানত কোমল থাকে, যা রাগটির মৃদু ছন্দ ও গম্ভীরতা বৃদ্ধি করে।
- ষড়ব–ষড়ব: আরোহ ও অবরোহে ছয়টি ছয়টি স্বর থাকার কারণে রাগটির মেলোডি বেশ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর অনুভূতি গভীর এবং প্রবল।
অন্যান্য তথ্য:
শিব সরস্বতী রাগের নাম থেকেই বোঝা যায় এটি দেবশক্তির প্রতি নিবেদিত। শিব ও সরস্বতী দেবী ভারতীয় সংস্কৃতির অতি গুরুত্বপূর্ণ দেবত্রী, যারা যথাক্রমে ধ্বনি ও জ্ঞানের প্রতীক। এই রাগে তাই সঙ্গীতের মাধ্যমে উচ্চতর আধ্যাত্মিক বোধ ও জ্ঞানের প্রেরণা পাওয়া যায়।
শিব সরস্বতী রাগটি মূলত হিন্দু-শাস্ত্রীয় সংগীতে ব্যবহৃত হলেও, আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে এটি আধুনিক সংগীত বা চলচ্চিত্র সংগীতেও অনুপ্রাণিত রূপে ব্যবহৃত হয়।
শিব সরস্বতী রাগ তার সরল অথচ গভীর সুরের কারণে শ্রোতাদের মধ্যে এক অনন্য প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি সৃষ্টি করে। এর গন্ধার ও ধৈবর্ত স্বরের কোমল ব্যবহার রাগটিকে বিশেষ করে তোলে, যা শ্রোতা ও শিল্পী উভয়ের জন্য একটি মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে।
রাগ-নির্ঝরিণী :
রাগ-নির্ঝরিণী হল ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীতের এক অনন্য এবং কম পরিচিত রাগ। এটি বিশেষত মোহনরাগ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং আভিজাত্য রাগটিকে আলাদা করে তোলে। শাস্ত্রীয় সংগীতে প্রতিটি রাগের নিজস্ব একটি আবেগ, ভঙ্গি ও সময় রয়েছে, আর নির্ঝরিণী সেই তালিকায় একটি প্রশান্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।
রাগের বৈশিষ্ট্য
রাগ-নির্ঝরিণীর আরোহ (উচ্চারণমালা) ও অবরোহ (নিম্নারণমালা) নিম্নরূপ:
- আরোহ: সা পা গা মা পা র্সা
- অবরোহ: সা দা পা মা গা মা য়া সা
এখানে, রাগটির বাদী স্বর হচ্ছে পঞ্চম (পা) এবং সমবাদী স্বর হচ্ছে ষড়জ, তবে এখানে ষড়জের স্থান নেই। এর ফলে রাগটির সৌন্দর্য এবং স্বতন্ত্রতা আরো বৃদ্ধি পায়।
রাগের অনুভূতি ও আবহ
নির্ঝরিণী শব্দের অর্থ “রাগ যা রাগিণীর হৃদয়ে ঝরিত পানির মত শান্তি এবং স্নিগ্ধতা আনে।” এই রাগের মাধুর্য এবং সুরের বৈশিষ্ট্য সাধারণত এক ধরণের গভীর প্রশান্তি এবং কোমলতার প্রতিফলন ঘটায়। এর সুরের ছোঁয়ায় মনে হয় যেন ঝুমঝুম বৃষ্টি নামে, জঙ্গলজুড়ে ঝুমঝুম শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।
গান-রুম বা তালের ছন্দ এমন একটি সৃষ্টি করে যা শুনলে মনে হয়, ঝুমঝুম রুম ঝুম্ শব্দগুলো শান্তির বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। এই রাগ সাধারণত ভোরের দিকে বা সন্ধ্যায় পরিবেশের সঙ্গে মানানসই হয়ে ওঠে, যখন প্রকৃতি ঘুম থেকে জেগে ওঠে বা ঘুমোন্ত বনভূমি চমকায়। তাই এই রাগ শ্রোতাকে এক ধরণের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ অনুভব করায়।
রাগ–নির্ঝরিণীর সঙ্গীত উদাহরণ
রাগের অনুভূতি বোঝাতে একটি সাধারণ গীতাংশের উদাহরণ দিচ্ছি:
“রুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম্ কে বজায়, জল ঝুমঝুমি চমকিয়া জাগে ঘুমন্ত বনভূমি।”
এই গানের মাধ্যমে প্রায়শই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও শান্তির অনুভূতি প্রকাশ করা হয়। সুরের গতি ও তাল রাগের বিশেষ মাধুর্যকে ফুটিয়ে তোলে, যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।
রাগ-নির্ঝরিণী ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি মূল্যবান রত্ন। এটি প্রশান্তির রাগ হিসেবে বিবেচিত এবং গভীর ধ্যান ও আবেগের প্রকাশ। যদিও এটি কম পরিচিত, তবে এর সৌন্দর্য এবং সুরের অনন্য গুণাবলী সঙ্গীত প্রেমীদের জন্য এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা।
রাগ-রূপমঞ্জুরী :
রাগ রূপমঞ্জরী হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি মনোরম রাগ, যা তার সুরেলা গঠন ও নান্দনিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত। এই রাগটি বিশেষত তার আরোহ-অবরোহের বিন্যাস, স্বরপ্রয়োগ এবং বাদী-সমবাদী স্বরের ব্যবহারে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।
🎼 রাগের গঠন ও বৈশিষ্ট্য
- আরোহ (Ascending): সা রে মা পা না সা
- অবরোহ (Descending): সা না ধা পা গা মা রে গা, সা রে না সা
- জাতি: ঔড়ব-সম্পূর্ণ (আরোহে ৫টি স্বর, অবরোহে ৭টি স্বর)
- বাদী স্বর: পঞ্চম (পা)
- সমবাদী স্বর: ষড়জ (সা)
- স্বরপ্রয়োগ: এই রাগে ব্যবহৃত সব স্বরই শুদ্ধ।
রাগ রূপমঞ্জরীর আরোহ-অবরোহের বিন্যাসে স্বরগুলির সুন্দর বিন্যাস ও ব্যবহারে একটি কোমল ও মধুর আবহ সৃষ্টি হয়। এই রাগটি শ্রোতাদের মনে এক প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।
🎶 রাগের ভাব ও অনুভূতি
রূপমঞ্জরী রাগটি মূলত প্রেম, স্নেহ ও কোমলতার অনুভূতি প্রকাশ করে। এর সুরেলা গঠন শ্রোতাদের মনে এক ধরণের প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতার আবহ সৃষ্টি করে। এই রাগে পরিবেশিত বন্দিশ বা গানগুলি সাধারণত প্রেমের অনুভূতি, প্রকৃতির সৌন্দর্য বা ভক্তির ভাব প্রকাশ করে।
🎵 উদাহরণস্বরূপ বন্দিশ
এই রাগে একটি জনপ্রিয় বন্দিশ:
“গান পায়েলা বোলে রিণিঝিণি, নাচে রূপমঞ্জরী শ্রীরাধার সঙ্গিনী“
এই বন্দিশে রাধার সঙ্গিনী রূপমঞ্জরীর নৃত্য ও তার পায়েলের শব্দের মাধ্যমে এক মনোরম দৃশ্যপট আঁকা হয়েছে, যা রাগটির কোমলতা ও স্নিগ্ধতা প্রকাশ করে।
রাগ রূপমঞ্জরী তার স্নিগ্ধতা, কোমলতা ও সুরেলা গঠনের জন্য হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য রাগ। এর পরিবেশনা শ্রোতাদের মনে এক প্রশান্তি ও মুগ্ধতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এই রাগটি সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
রাগ-অরুণ রঞ্জনী:
রাগ অরুণ-রঞ্জনী কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্ট একটি অনন্য রাগ, যা তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। এই রাগটি মূলত তাঁর ‘নবরাগমালিকা’ গীতিনাট্যের অংশ হিসেবে রচিত হয়েছিল এবং প্রথম প্রচারিত হয় ১৯৪০ সালের ১১ মে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে।
🎼 রাগের গঠন ও স্বরবিন্যাস
- জাতি: ঔড়ব-ষাড়ব (আরোহে পাঁচটি স্বর, অবরোহে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত)
- আরোহ: সা, গা, পা, ধা, সা
- অবরোহ: সা, নি, ধা, পা, গা, রে, সা
- বাদী স্বর: পঞ্চম (পা)
- সমবাদী স্বর: ষড়জ (সা)
- বিশেষত্ব: রে, গা, ধা, এবং নি স্বরগুলি কোমল এবং মাধ্যাম (মা) তীব্ররূপে ব্যবহৃত হয়।
এই রাগের স্বরবিন্যাসে কোমল ও তীব্র স্বরের সংমিশ্রণ একটি বিশেষ আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা প্রভাতের সূর্যোদয়ের কোমলতা ও উজ্জ্বলতাকে প্রতিফলিত করে।
🌅 পরিবেশনের সময় ও রস
রাগ অরুণ-রঞ্জনী মূলত অতি-প্রত্যুষে পরিবেশনের জন্য উপযুক্ত, যখন আকাশে শুকতারা হাস্যজ্জ্বল দ্যুতি ছড়ায় এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে প্রভাতের কোমল আলো ছড়িয়ে পড়ে। এই রাগে শৃঙ্গার রসের গভীর অনুভব প্রকাশ পায়, যা প্রেম, প্রত্যাশা এবং প্রভাতের সৌন্দর্যকে সঙ্গীতের মাধ্যমে উপস্থাপন করে।
🎵 নজরুলের গান: “হাসে আকাশে শুকতারা হাসে”
এই রাগে রচিত নজরুলের গান “হাসে আকাশে শুকতারা হাসে” রাগ অরুণ-রঞ্জনীর সৌন্দর্য ও আবেগকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরে। গানটি ‘নবরাগমালিকা’র দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় গান হিসেবে পরিবেশিত হয়েছিল। এতে প্রভাতের সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তের সৌন্দর্য এবং প্রেমের অনুভবকে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।
রাগ অরুণ-রঞ্জনী কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত প্রতিভার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। এই রাগের মাধ্যমে তিনি প্রভাতের সৌন্দর্য, প্রেমের অনুভব এবং সঙ্গীতের গভীরতা একত্রিত করেছেন। নজরুলের এই সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা সঙ্গীতের ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

রাগ-দেবযানী:
বাংলা সংগীতের জগতে কাজী নজরুল ইসলাম শুধুমাত্র কবি ও গীতিকার হিসেবেই নয়, একজন সুরস্রষ্টা হিসেবেও অমর। তিনি বাংলা সংগীতে রাগসংগীতের ধারা প্রবাহিত করেছেন এবং নতুন রাগ সৃষ্টির মাধ্যমে সংগীত জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তাঁর সৃষ্ট রাগগুলোর মধ্যে ‘দেবযানী’ একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
🎵 রাগ দেবযানীর সংগীত বৈশিষ্ট্য
- আরোহ (উর্ধ্বগমন): সা রা পা পা ধা রা পা, ণা ধা নাসা
- অবরোহ (নিম্নগমন): সা ণা ধা পা রা সা
- জাতি: ঔড়ব-ঔড়ব (উর্ধ্ব ও নিম্নগমনে পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত)
- বাদী স্বর: পঞ্চম (পা)
- সমবাদী স্বর: ঋষভ (রে)
- স্বর বৈচিত্র্য: এই রাগে কেবলমাত্র ‘নি’ স্বরটি কোমল; অন্যান্য সব স্বর শুদ্ধ।
এই রাগের স্বরবিন্যাসে কোমল ‘নি’ এর ব্যবহার রাগটির মাধুর্য ও কোমলতা বৃদ্ধি করে, যা শ্রোতার মনে এক গভীর আবেগ সৃষ্টি করে।
🧠 রাগের নামকরণ ও পৌরাণিক প্রেক্ষাপট
‘দেবযানী’ নামটি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির একটি চরিত্রের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। মহাভারতের আদি পর্বে কচ ও দেবযানীর উপাখ্যানে দেবযানী ছিলেন অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। কচ, দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির পুত্র, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অর্জনের জন্য শুক্রাচার্যের আশ্রমে আসেন। এই সময়ে দেবযানী কচের প্রতি প্রেমে পড়েন। কচ বিদ্যা অর্জনের পর দেবযানীর প্রেমপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, যা দেবযানীকে কষ্ট দেয়। এই কাহিনির আবেগ ও নাটকীয়তা নজরুলকে অনুপ্রাণিত করে রাগ ‘দেবযানী’ সৃষ্টি করতে।
🎶 গান: “দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে”
এই রাগে রচিত নজরুলের একটি বিখ্যাত গান হলো “দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে”। এই গানটি ১৯৪০ সালের ১১ মে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ‘নব রাগমালিকা’ গীতিনাট্যের দ্বিতীয় পর্বে প্রথম গান হিসেবে পরিবেশিত হয়। গানটির সুরারোপ করেন নজরুল নিজেই এবং স্বরলিপি রচনা করেন জগৎ ঘটক।
গানটির সুর ও ছন্দে নজরুল নতুনত্ব এনেছেন। তিনি ‘নবনন্দন’ নামক একটি নতুন ছন্দের প্রয়োগ করেছেন, যা ২০ মাত্রার তাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ছন্দ ও সুরের সংমিশ্রণে গানটি একটি অনন্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।
🎼 রাগ দেবযানীর সংগীতিক বিশ্লেষণ
রাগ দেবযানী একটি ঔড়ব-ঔড়ব জাতির রাগ, যার আরোহ ও অবরোহে পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হয়েছে। এই রাগে ‘নি’ স্বরটি কোমল এবং অন্যান্য সব স্বর শুদ্ধ। বাদী স্বর পঞ্চম (পা) এবং সমবাদী স্বর ঋষভ (রে)। এই রাগের স্বরবিন্যাস ও চলন রাগটির একটি বিশেষ আবেগময়তা ও কোমলতা প্রদান করে, যা শ্রোতার মনে এক গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে।
রাগ দেবযানী নজরুলের সৃষ্ট এক অনন্য রাগ, যা বাংলা সংগীতে তাঁর অবদানকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এই রাগের মাধ্যমে নজরুল তাঁর সুরসৃষ্টি ও ছন্দের নতুনত্ব প্রদর্শন করেছেন। রাগ দেবযানী ও এর উপর ভিত্তি করে রচিত গানগুলি বাংলা সংগীতের ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।
রাগ-দোলন চাঁপা :
রাগ দোলনচাঁপা হাম্বীর, কামোদ ও নট রাগের আভাস বহন করে, তবে তার নিজস্ব দোলনশীল গতি ও সুরের মাধুর্য তাকে স্বতন্ত্র করে তোলে। আরোহে সুরের ‘ঝুলনা’ বা দোলন এই রাগের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা দোলনচাঁপা ফুলের দোলার মতো সুরের দোলায় শ্রোতাকে মুগ্ধ করে।
🎼 রাগ দোলনচাঁপা: গঠন ও বৈশিষ্ট্য
আরোহ: সা গা হ্মা পা, গা মা না ধা, পা না ধা সা
অবরোহ: সা না ধা না ধা পা হ্মা, পা, গা মা রা সা
জাতি: ষাড়ব-সম্পূর্ণ (আরোহে ৬টি, অবরোহে ৭টি স্বর)
বাদী স্বর: পঞ্চম (পা)
সম্বাদী স্বর: ষড়জ (সা)
বিশেষত্ব: এই রাগে ‘মা’ স্বরটি তীব্র ও শুদ্ধরূপে ব্যবহৃত হয়, যা রাগের মাধুর্য ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে।
দোলনচাঁপা’ নামটি এই রাগের সুরের দোলনশীলতা ও মাধুর্যের প্রতীক। দক্ষিণ সমীরণে দোলনচাঁপা ফুলের দোলার সঙ্গে এই রাগের সুরের গতি ও মাধুর্যের সামঞ্জস্য রয়েছে। তীব্র মধ্যম ও ‘গা মা না ধা’ সুরের সংমিশ্রণে চাঁপা ফুলের সুরভির তীব্রতা ও মাধুর্য ফুটে ওঠে।
নজরুলের সৃষ্ট রাগ দোলনচাঁপায় নিবদ্ধ ‘দোলনচাঁপা বনে দোলে’ গানটি তাঁর ‘নব রাগমালিকা’ গীতিনাট্যের অংশ। ১৯৪০ সালের ১৩ জানুয়ারি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে এই গীতিনাট্যের প্রথম পর্ব প্রচারিত হয়, যেখানে এই গানটি ষষ্ঠ গান হিসেবে পরিবেশিত হয়। গানটির স্থায়ীতে দোলনের আনন্দকে কবি তুলে ধরেছেন, যেন পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সঙ্গে দোলনচাঁপা ফুল দোল খায়। এই গানটি দোলনচাঁপা রাগের রূপক-লক্ষণগীত হিসেবে বিবেচিত হয়।
📚 গ্রন্থ ও রচনাকাল
গ্রন্থ: ‘নজরুল গীতি, অখণ্ড’ (সম্পাদনা: আব্দুল আজীজ আল-আমান, প্রকাশক: হরফ প্রকাশনী)
রচনাকাল: ১৯৪০ সালের ১৩ জানুয়ারি, কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে ‘নব রাগমালিকা’ গীতিনাট্যের প্রথম পর্ব প্রচারিত হয়, যেখানে এই গানটি ষষ্ঠ গান হিসেবে পরিবেশিত হয়।
রাগ-মীণাক্ষী :
কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সঙ্গীতের জগতে এক অনন্য নাম, যিনি কেবল কবিতা ও গানেই নয়, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ রচনাতেও অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি প্রায় ৩০টিরও বেশি রাগ সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে ‘রাগ-মীণাক্ষী’ একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই রাগটি তাঁর সৃষ্টিশীলতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন, যা বাংলা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।
রাগ–মীণাক্ষীর গঠন ও বৈশিষ্ট্য
- আরোহ (উর্ধ্বগমন): ণা ধা সা ণা রা, গা মা পা গা মা পা ধা র্সা
- অবরোহ (অধোগমন): সা ণা ধা মা পা, দা পা মা জ্ঞা রা, গা সা
- জাতি: সম্পূর্ণ (সপ্ত স্বরযুক্ত)
- গতির ধরন: বক্রগতি (স্বরের চলন সরল নয়, বাঁকযুক্ত)
- বাদী স্বর: ঋষভ (রে)
- সমবাদী স্বর: পঞ্চম (পা)
এই রাগে অবরোহে ‘নি’ স্বরটি কোমল রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং ‘গ’ ও ‘ধ’ স্বর দুটি কোমল ও শুদ্ধ উভয় রূপেই প্রয়োগ পায়। এটি রাগটির সুরের গভীরতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে।
রাগ–মীণাক্ষীর সঙ্গীতিক রূপ
নজরুলের রচিত গান “চপল আঁখির ভাষায়, হে মীণাক্ষী ক’য়ে যা / না-বলা কোন্ বাণী বলিতে চাও” এই রাগে সুরারোপিত। গানটির সুর ও ভাব রাগ-মীণাক্ষীর বৈশিষ্ট্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, যেখানে কোমল ও শুদ্ধ স্বরের সংমিশ্রণ একটি মায়াবী আবহ সৃষ্টি করে।
রাগ–মীণাক্ষীর সঙ্গীতিক বিশ্লেষণ
রাগ-মীণাক্ষী একটি সম্পূর্ণ ও বক্রগতির রাগ, যার আরোহ ও অবরোহে স্বরের চলন সরল নয়, বরং বাঁকযুক্ত। এটি রাগটির সুরের গভীরতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে। বাদী স্বর ঋষভ (রে) এবং সমবাদী স্বর পঞ্চম (পা) হওয়ায়, রাগটির মূল আবেগ ও রস এই স্বরগুলির উপর নির্ভরশীল। অবরোহে কোমল ‘নি’ এবং ‘গ’ ও ‘ধ’ স্বরের কোমল ও শুদ্ধ রূপের ব্যবহার রাগটির সুরে একটি মায়াবী আবহ সৃষ্টি করে।
নজরুলের রাগ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট
নজরুল ইসলাম বাংলা সঙ্গীতে প্রায় ৩০টিরও বেশি রাগ সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ। রাগ-মীণাক্ষী এই রাগগুলির মধ্যে একটি, যা তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগের প্রতিফলন। এই রাগগুলি বাংলা সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে নজরুলের অবদানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।
রাগ-মীণাক্ষী কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত প্রতিভার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই রাগের মাধ্যমে তিনি বাংলা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও সঙ্গীতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। রাগ-মীণাক্ষী তাঁর সঙ্গীতকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
নজরুল সৃষ্ট তাল
কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি ও সঙ্গীতের বিস্ময়কর প্রতিভা, কেবল শব্দের খেলাতেই নয়, সুর ও ছন্দের বৈচিত্র্যেও এক অভূতপূর্ব উদ্ভাবক। তাঁর সৃষ্ট তালগুলি বাংলা সঙ্গীতকে দিয়েছে নতুন মাত্রা ও জীবন, যেখানে প্রতিটি বিটে মিশে আছে মুক্তির জয়গান, প্রেমের কোমলতা, এবং সংগ্রামের দৃপ্ত আহ্বান। নজরুলের তালের বিন্যাসে যেমন পাওয়া যায় প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ছোঁয়া, তেমনই রয়েছে নতুন যুগের সাহসী ছন্দের প্রতিচ্ছবি। তাঁর সৃষ্ট তালের প্রতিটি ছন্দে যেন ধ্বনিত হয় মানুষের জাগরণ, প্রেমের উচ্ছ্বাস, এবং স্বাধীনতার স্পন্দন। নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত গানে তালের বৈচিত্র্যতার জন্যে ৬টি তাল সৃষ্টি করেন, তালগুলো নিম্নরূপ:
১. প্রিয়াছন্দ তাল:
কাজী নজরুল ইসলাম এর সৃষ্ট ‘প্রিয়া ছন্দ তাল’ বাংলা তালের ভাণ্ডারে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন, যা তাঁর ছন্দ ও সংগীতচর্চার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।
‘প্রিয়া ছন্দ তাল’ কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্ট একটি তবলার তাল, যা ৭ মাত্রার একটি বিষমপদী তাল। তালটির ছন্দোবিভাজন ২।৩।২ এই রূপে গঠিত, যা একে অন্যান্য প্রচলিত তালের তুলনায় স্বতন্ত্র করে তোলে। তালটির বোল বিন্যাস নিম্নরূপ:
ধিন না | ধিন ধিন না | তিন না
এই বোল বিন্যাসে কোনো ফাঁক (খালি) নেই এবং তিনটি তালি রয়েছে, যা তালটির গঠনকে আরও দৃঢ় করে তোলে।
১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই (শনিবার, ১০ শ্রাবণ ১৩৪৮) কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ‘ছন্দিতা’ নামক একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সৃষ্ট ‘প্রিয়া ছন্দ তাল’ উপস্থাপন করেন। এই তালটি সংস্কৃত ‘প্রিয়া ছন্দ’-এর অনুসরণে রচিত, যা নজরুলের ছন্দ ও সংগীতচর্চার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
গান : মহুয়া বনে বন পাপিয়া।
২. মনিমালা ছন্দ তাল:
মাত্রা সংখ্যা: ২০
ছন্দ বিন্যাস: ২।৪।২।২।২।৪।২।২
মাত্রা বিন্যাস: ১২। ৩৪৫৬। ৭৮। ৯১০। ১১১২। ১৩১৪১৫১৬। ১৭১৮। ১৯২০
এই ছন্দে মোট ২০টি মাত্রা রয়েছে, যা আটটি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা রয়েছে, যা কবিতার ছন্দময়তাকে নির্ধারণ করে। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো এর সুনির্দিষ্ট মাত্রা বিন্যাস, যা কবিতায় একটি নির্দিষ্ট ছন্দগত গতি ও সুর প্রদান করে।
গান: মনজু মধুছন্দা নিত্য তব সঙ্গী
৩. মঞ্জু ভাষিনী ছন্দ :
মঞ্জু ভাষিনী ছন্দ হলো নজরুলের উদ্ভাবিত একটি ছন্দের ধরন, যা স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ মাত্রা ও তাল কাঠামোর দ্বারা চিহ্নিত। এ ছন্দে ব্যবহৃত মাত্রা সংখ্যা হলো ১৮, যা ভেঙে দেয়া যায় নিম্নরূপ:
- মাত্রার সংখ্যা: ১৮ (বিভক্তি: ২। ৩। ৫। ৩। ৩(২))
এখানে “২”, “৩”, “৫”, “৩”, “৩(২)” মানে, মোট ১৮ মাত্রাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে ছন্দ তৈরি হয়েছে। এর প্রতিটি ভাগ নির্দিষ্ট মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত, যা পাঠক বা শ্রোতাকে একটি সুরেলা ও স্বাভাবিক তালবদ্ধতা দেয়।
নজরুল সৃষ্ট মঞ্জু ভাষিনী ছন্দের তালটি নিচের মতো:
- ছন্দ ১২
- ৩৪৫
- ৬৭৮৯১০
- ১১১২১৩
- ১৪১৫১৬
- ১৭১৮
এই তালের মাধ্যমে কবিতায় ছন্দের ছন্দোবদ্ধতা, তালবদ্ধতা এবং স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা হয়।
কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতাকে গীতিময় করে তোলেন তাঁর ছন্দের অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য ও উদ্ভাবনী শৈলীর মাধ্যমে। তিনি বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধরণের ছন্দ ও তাল সৃষ্টি করেন যা বাংলা কবিতাকে এক নতুন প্রাণ ও জীবন দেয়। নজরুলের ছন্দগুলো কেবলমাত্র মাত্রা ও তাল নয়, বরং কবিতার ভাব, গতি, এবং আবেগকে সঙ্গীতময় করে তুলে।
মঞ্জু ভাষিনী ছন্দের মতো ছন্দগুলো বাংলা কবিতার ছন্দতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এর মাধ্যমে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাকে বিস্তৃত করেছেন, যেখানে ছন্দের স্বাধীনতা এবং সৃজনশীলতার মিশেল দেখা যায়।
এই ছন্দটি নজরুলের গীতিগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মঞ্জু ভাষিনী ছন্দের ব্যবহারে কবিতার ছন্দ এবং গানের তাল একত্রিত হয়ে পাঠকের মনে গভীর সুরের ছাপ ফেলে। ফলে কবিতার আবেগ-উন্মেষ অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়।
বাংলা ছন্দতত্ত্বে মঞ্জু ভাষিনী ছন্দ একটি উদ্ভাবনী এবং শিল্পসম্মত পদক্ষেপ। এটি নজরুলের বহুমাত্রিক প্রতিভার এক জ্বলন্ত প্রমাণ, যা বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ছন্দের ব্যবহার বাংলা কবিতায় ছন্দ ও তালের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।
৪. স্বাগতা ছন্দ :
“স্বাগতা ছন্দ” নজরুলের রচনায় ব্যবহৃত একটি ছন্দ যা মাত্রা ও ছন্দ বিন্যাসের মাধ্যমে গঠিত। এই ছন্দের মাত্রা সংখ্যা মোট ১৬, যা ভেঙে পড়ে ৩, ৫, ৪, ২, ২ মাত্রায়। অর্থাৎ,
মাত্রা সংখ্যা: ১৬ (৩ + ৫ + ৪ + ২ + ২)
এটি একটি জটিল এবং সুষম ছন্দ, যা কবিতায় সুর ও গতি প্রদান করে।
ছন্দের বিন্যাসটি এভাবে দেওয়া হয়:
| ১২৩ | ৪৫৬৭৮ | ৯১০১১১২ | ১৩১৪ | ১৫১৬ |
এখানে প্রতিটি সংখ্যা একটি মাত্রা নির্দেশ করে এবং গোষ্ঠীগুলো ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ। এই ছন্দ বিন্যাস কবিতাকে একটি নির্দিষ্ট সুর ও ছন্দের ধারা প্রদান করে যা পাঠক ও শ্রোতার মনে ছাপ ফেলে।
নজরুলের সঙ্গীত ও কবিতায় তালের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রচুর রাগিনীতে তাল ও ছন্দের বিভিন্ন রূপ আবিষ্কার করেছেন। “স্বাগতা ছন্দ” ছাড়াও তিনি অনেক নতুন ছন্দ ও তালের উদ্ভাবন করেছেন যা বাংলা কাব্য ও সঙ্গীতকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।
নজরুল সঙ্গীতে ছন্দ ও তাল প্রায়শই রাগ ও ছন্দের সাথে মিলিত হয়ে একটি দারুণ সুরের সৃষ্টি করে। তাঁর কাব্যে তাল শুধুমাত্র ছন্দের মাপকাঠি নয়, এটি আবেগ ও ভাবের বহিঃপ্রকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
গান : স্বাগতা নককচম্পক বর্ণা।
৫. মন্দাকিনী ছন্দ:
“মন্দাকিনী” শব্দটি মূলত একটি নদীর নাম, যা প্রাচীন কালের কবিতায় মিষ্টি সুর ও স্নিগ্ধতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নজরুলের এই ছন্দের নামকরণ হয়েছিলো সেই নদীর নাম অনুসারে, যার ধারায় যেমন মাধুর্য ও কোমলতা প্রবাহিত হয়, তেমনি এই ছন্দের গতি ও মাত্রার ধরণ পাঠকের হৃদয়ে সুমিষ্ট সংগীতময় ছন্দ প্রবর্তন করে।
মন্দাকিনী ছন্দের মাত্রা সংখ্যা হলো ১৬। অর্থাৎ, কবিতার প্রতিটি পঙক্তিতে মোট ১৬ টি মাত্রা বা মেট্রিক্যাল ইউনিট থাকে। এই মাত্রাগুলি ছন্দবদ্ধভাবে বিন্যস্ত হয়, যা নিম্নরূপ:
- মাত্রার গঠন: ৬াত।হাত।২ (৬ মাত্রার একত্রে, তার পর ১ মাত্রার হাত, এবং শেষে ২ মাত্রার অংশ)
- ছন্দবিন্যাস: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
অর্থাৎ, ছন্দের প্রথম অংশে ৬ মাত্রার একটি ‘হাত’ এবং পরবর্তীতে ১ মাত্রার একটি ‘হাত’ এবং শেষে ২ মাত্রার অংশ মিলেমিশে এই মন্দাকিনী ছন্দের কাঠামো গঠন করে।
নজরুল মন্দাকিনী ছন্দ ব্যবহার করে যে কবিতা ও গানে গভীর ছন্দসঙ্গীত এবং বাণীবহুলতা সৃষ্টি করেছেন, তা বাংলা কবিতার ধারায় এক অনন্য সংযোজন। মন্দাকিনী ছন্দের মাধ্যমে তিনি প্রথাগত ছন্দের বাইরেও গীতিময় এবং গরিমাময় কবিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ছন্দের মাধুর্য পাঠক ও শ্রোতাদের হৃদয়ে একটি বিশেষ ধরনের সুরেলা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।
মন্দাকিনী ছন্দের বৈশিষ্ট্য
- স্বরলিপি ও ছন্দবদ্ধতা: ছন্দের মাত্রাগুলি সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত থাকায় এটি পড়তে ও গাইতে সহজ এবং মাধুর্যময় হয়।
- বৈচিত্র্য: নজরুল এই ছন্দে নানা রকম ভাব প্রকাশ করেছেন, যা বিভিন্ন ধরণের কবিতা ও গানের জন্য উপযুক্ত।
- লয় ও গতি: মন্দাকিনী ছন্দে নির্দিষ্ট মাত্রার পুনরাবৃত্তির কারণে ছন্দের একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যা শুনতে খুব মনোমুগ্ধকর।
গান : জল ছল ছল এস মন্দাকিনী।
৬. নবনন্দনঃ
বাংলা সংগীত-সাহিত্যের অমর কীর্তি কাজী নজরুল ইসলামের গানগুলোতে তাল এবং ছন্দের এক অনন্য ছাপ রয়েছে। তাঁর সৃষ্ট তাল ও ছন্দবিন্যাস বাংলা গানের ধারাকে বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল করেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ তাল হলো “নবনন্দন”, যা নজরুল সঙ্গীতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।
নবনন্দন তাল একটি বিশেষ ছন্দের তাল যেখানে মোট মাত্ৰা বা তালবিন্দু সংখ্যা ২০। এটি নজরুলের নিজস্ব আবিষ্কার এবং তাঁর সৃষ্টিশীলতার এক সুন্দর উদাহরণ। নবনন্দন তাল মূলত কাব্যিক ছন্দের নিরিখে সাজানো হয়েছে, যা বাংলা গানের সুর ও ছন্দের সঙ্গে অত্যন্ত সুসঙ্গত।
নবনন্দন তালের মাত্ৰাসংখ্যা ২০, যা নিচের মতো বিভক্ত:
- মাত্ৰাসংখ্যা: ২০ (৪৪৮১৮১৮)
- ছন্দ বিন্যাস:
১২৩৪৫৬৭৮
৯১০১১১২
১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০
এখানে মাত্ৰাগুলোর মিশ্রণ এবং ছন্দের বিন্যাস নজরুলের গানের কাব্য ও সঙ্গীতশৈলীর অনন্য দিক তুলে ধরে। এই তালের ছন্দ-লয়ের জাদু নজরুলের গানে রাগীন অনুভূতি ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।
নবনন্দন তাল সঙ্গীতে ব্যতিক্রমধর্মী এবং এটি সঙ্গীতের গতি ও ছন্দকে এক নতুন মাত্রা দেয়। এর মাধ্যমেই নজরুল ইসলামের গানগুলোতে এক অনন্য ছন্দের ছোঁয়া লেগেছে, যা শ্রোতাদের মনকে মুগ্ধ করে।
বাংলা আধুনিক গানের ক্ষেত্রে নবনন্দন তালের প্রয়োগ নজরুলকে একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী ও রচয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই তাল ব্যবহার করে তিনি যে ছন্দবদ্ধ গীতিকাব্য রচনা করেছেন, তা বাংলার সঙ্গীত ঐতিহ্যের জন্য এক অসাধারণ উপহার।
গান : দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে।
আরও পড়ুন: