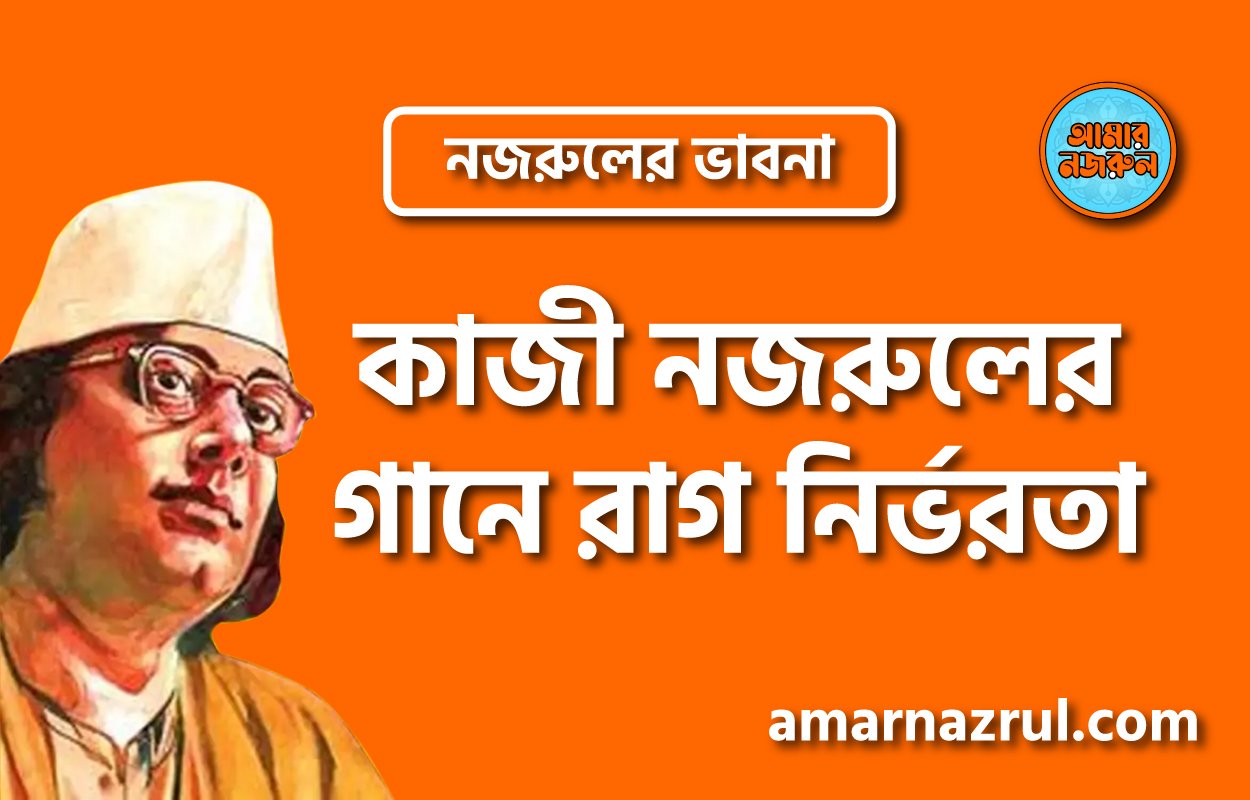কাজী নজরুলের গানে রাগ নির্ভরতাঃ সঙ্গীতস্রষ্টা নজরুলের জীবনে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হলো রাগ সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর ভক্তি ও নিষ্ঠা। রাগ রাগিনীর প্রয়োগ ও ব্যবহারে নজরুল তাঁর অনুপম সৃজনীশক্তির পরিচয় নিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তাদের প্রয়োগরীতিতে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি কোথাও না লঙ্ঘন করে তিনি মহত্তর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কাজী নজরুলের গানে রাগ নির্ভরতা । নজরুলের ভাবনা
পূরবী, বেহাগ, বা জয়জয়ন্তী, যে-কোনো রাগের ক্ষেত্রেই তার চলন, সুরবিস্তার প্রভৃতি পালন করেছেন। শিল্পীমনের নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় তিনি প্রচলিত রাগ রাগিনীর রূপান্তর না ঘটিয়ে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। নজারুলকৃত নবরাগমালিকা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত এবং কবি সেগুলির যাবতীয় পরিচয় প্রদান করে গেছেন।
দুই-তিনটি প্রচলিত রাগকে যে মুন্সীমায়নায় মিশ্রিত করে তিনি নতুন সুরের মেজাজ সৃষ্টি করেছেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। “ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান’-বেহাগ ও বসন্তের মিশ্রণে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে।
নজরুল-কৃত নবরাগ প্রসঙ্গে প্রথমে ধরা যাক, ‘দোলন চাঁপা’ রাগিণীর কথা। এখানে হাম্বীর কামোদ ও নট, তিনটি রাগের রূপই মাঝে মাঝে উকি দেয়। রাগের চঞ্চল গতির কারণে ঐ আভাস স্থায়ী হয় না। আরোহী স্বর সা গা ক্ষা পা, গামা না ধা, পা, না, ধার্সা, অবরোহণে ব্যবহৃত হয়েছে সা না ধাণা, ধা পা ধা পা ক্ষ পা গা মা গা মা রা না।

ধৈবত ও বড় যথাক্রমে বাদী ও সম্বাদী। কবিকল্পনায় রাগটির মাধ চাঁপাফুলের সুরভির মতো তীব্র এবং সেখানেই নামকরণের সার্থকতা। এই তীব্র সুরভি ক্ষা, গা মা না ধা ব্যবহারে প্রকাশিত। অনুরূপভাবে ‘মীনাক্ষী; রাগিনীতে নীলাম্বরী, কাফি আভাস পাওয়া যায়। রাগিনীতে মীনের বক্র ও চঞ্চল গতি ফুটে ওঠে অবরোহনে কোমল ধৈবতোর মাধ্যমে ঘেঁষা গান্ধারের ব্যবহারে।
কাজী সাহেব রাগ রাগিনীর এই বৃহৎ ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন সূত্রে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে তিনি ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খানের সান্নিধ্যে আসেন এবং কার্যত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ-নিবাসী ওস্তাদ কাদের বক্স ও মঞ্জু সাহেবের নিকটও তিনি বহু রাগ রাগিনী আয়ত্ত করেন। ঠাকুর নবাব আলী চৌধুরী প্রণীত সঙ্গীত-পুস্তক থেকে তিনি বহু অপ্রচলিত ও প্রায় রাগ রাগিনীর হদিশ পান।
উদাহরণ হিসাবে লংকাদহন সারং রাগটি ধরা যায়। এই রাগে নজরুল রচনা করেন “অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া’ গানটি। একইভাবে রচিত হল মেঘবিহীন খর বৈশাখে’ গানটি সাবস্ত শারং রাগে। এই পথে আহরিত হয় বিরাট ভৈরব, দরবারী টোড়ী, বড়হংস সারং, দেবগান্ধার প্রভৃতি রাগ। এ-ছাড়া প্রথম শ্রেণীর শ্রুতিধর হওয়ার ফলে অনেক অনুপম নজরুলসঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে।
সে যুগের বিখ্যাত অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের গাওয়া ‘নীলাম্বরী” রাগের বিখ্যাত গান শুনে তিনি রচনা করলেন ‘নীলাম্বরী’ শাড়ি পরি নীল যমুনায় কে যায় গানটি। ‘কাবেরী তীরে’ ও ‘হরপ্রিয়া’ নামে দুটি বেতারগীতি আলেখ্যে তিনি গানটি যুক্ত করেন। পরবর্তীকালে কবির পরিচালনায় ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র রেকর্ডে গানটি পরিবেশন করে অবিনশ্বর মর্যাদা দান করেছেন।

কয়েক হাজার নজরুলসঙ্গীতে শতাধিক রাগ রাগিনীর ব্যবহৃত হয়েছে। প্রচলিত, লুপ্তপ্রায় এবং স্ব-কৃত রাগ রাগিনীর অগুলিতে তিনি সাজিয়েছিলেন দেবী সুরেশ্বরীর বরণডালা। এ এক বিস্ময়কর নজীর রাগভিত্তিক বেশ কিছু নজরুলসঙ্গীত বাংলাগানের শ্রোতাদের কাছে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারেঃ
‘শুন্য এ বুকে পাখি মোর’ (ছায়ানাট), “শ্মশানে জাগিছে, শ্যামা’ (কৌশিকী), ‘অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী’ (আহির ভৈরব), ‘কুহু কুহু কোয়েলিয়া’ (খাম্বাজ) ‘কারেবী নদীজলে কে গো বালিকা (কণটী সামন্ত), ‘কেউ ভোলে না কেউ ভোলে’ (মান্দ), ‘আজি ও শ্রাবণ নিশি’ (মিয়া মল্লার), ভোরের হাওয়ায় এলে’ (রামকেলি), গুঞ্জমালা গলে’ (মালগুঞ্জি), ‘ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি (হিজাজ ভৈরবী), ‘রুমঝুম রুমঝুম’ (পিলু) প্রভৃতি।
সঙ্গীত-শিক্ষক নজরুলের অভিনব শিক্ষা পদ্ধতিতে কোনো গোঁড়ামি ছিল না। তিনি শিল্পীর গান শুনে তার গায়ন-রীতি বা অধিকারটুকু বুঝে নিয়ে তার উপযোগী গান দিতেন। শিল্পীর সবটুকু উৎকর্ষ তিনি গানের মধ্যে আদায় করে নিতেন। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, শচীন দেববর্মণ, মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীমতী ইন্দুবালা, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখ শিল্পীরা স্ব-স্ব রীতিতে জ্যোতিষ্মান।
নজরুল এঁদের প্রত্যেকের গানে অলঙ্করণ পদ্ধতির বিভিন্নতায় তাঁদের শিল্পী মেজাজের স্বাধীনতাকে সুযোগ দিয়েছেন পরিপূর্ণ গায়কী আদায়ের জন্য। শচীনবাবুর ‘পদ্মার ঢেউরে’ বা ‘কুহু কুহু কোয়েলিয়া’, মৃণালকান্তির ‘বলরে জবা বল’ বা ‘মহাকালের কোলে এসে’ এবং শ্রীমতী ইন্দুবালার ‘কেন আন ফুলডোর’ ‘অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে’ গানের চালে দুস্তর ব্যবধান। অনুমান করা কঠিন যে সবগুলিই নজরুলের সৃষ্টি। আবার তাঁর সঙ্গীতজীবনের শেষ পর্বের বিশিষ্ট শিল্পী শৈলদেবীর গাওয়া গানে আমরা পাই আরেক নজরুলকে।

১৯২২-৪২ এই কুড়ি বছরে নজরুল যে কত শিল্পীকে দিয়ে তাঁর গান রেকর্ড করিয়েছেন তা সঠিকভাবে নিরুপণ করা সম্ভব নয়। একটি আংশিক তালিকা থেকেই নজরুলসঙ্গীতের বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাবে ললিত মুখোপাধ্যায়, কে মল্লিক, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, গোস্বামী, উমাপদ ভট্টাচার্য, ধীরেন দাস, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মণ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, মৃণালকান্তি ঘোষ, রত্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু দত্ত, কমল দাশগুপ্ত, গিরীন চক্রবর্তী, চিত্ত রায়, সত্য চৌধুরী, সত্যেন ঘোষাল, জনন্ময় মিত্র, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন চৌধুরী, গোপাল সেন, সুনীল ঘোষ, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, হরিমতী, কমলা ঝরিয়া), রাধারাণী, বীণাপানি (মধুপুর), শৈল দেবী, ইলা ঘোষ, দীপালি নাগ, সুপ্রভা সরকার, যূথিকা রায়, কানন দেবী, মড় কস্টেলো, পারুল দাস (কর), গীতা মিত্র, বিজন ঘোষ দস্তিদার, কুসুম গোস্বামী, প্রতিভা বসু (সাহিত্যিক), দীপ্তি বন্দোপাধ্যায়, কল্যাণী দাস প্রমুখ।