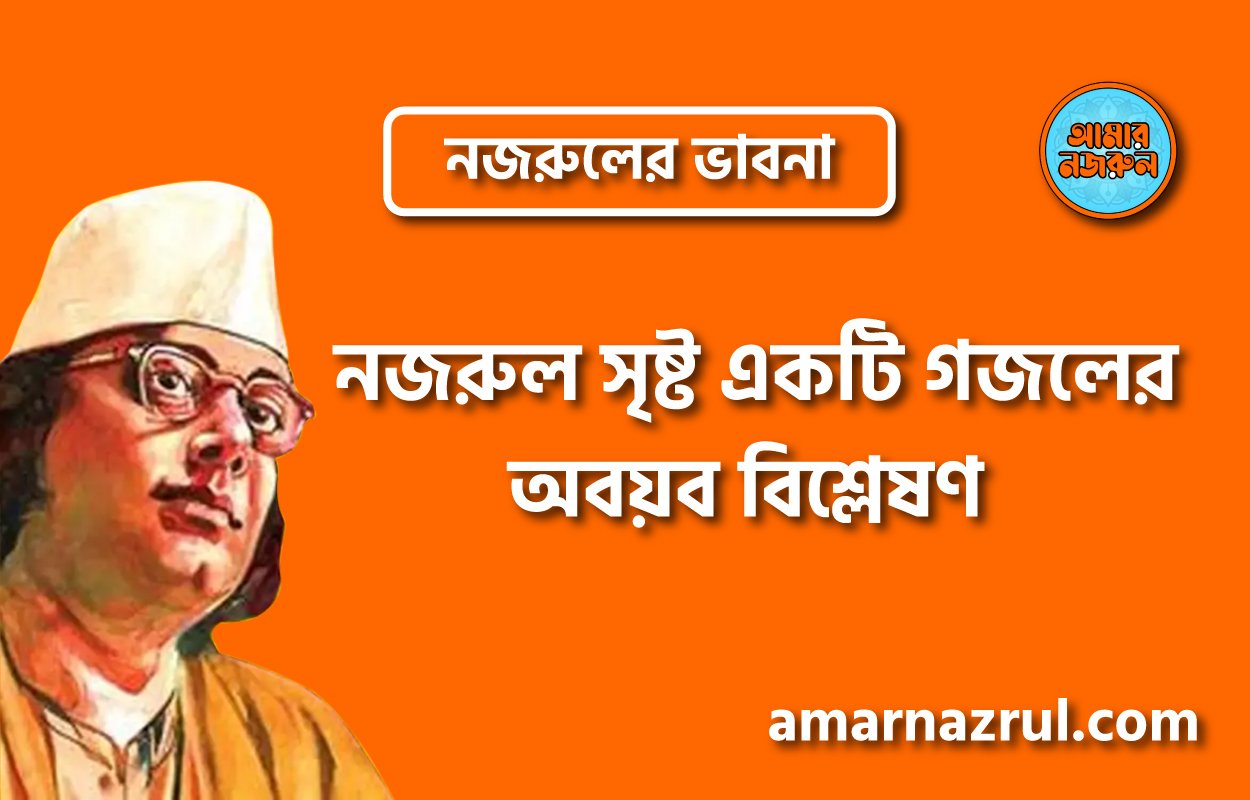নজরুল সৃষ্ট একটি গজলের অবয়ব বিশ্লেষণ : গজল গানে কথা বেশি, সুরের প্রাধান্য কম। মূলত হালকা ধরনের গান হলেও সব ধরনের রচনাই এ গানের বিষয়বস্তু হতে পারে। উচ্চভাবপূর্ণ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ রচনাও কোন কোন গানে দেখা যায়। এ গানে অনেকগুলো চরণ, কলি বা তুক্ থাকে।

নজরুল সৃষ্ট একটি গজলের অবয়ব বিশ্লেষণ
গানের বাণীঃ
বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
- রচনাকালঃ ১৩৩৩
- স্থান কৃষ্ণনগর (মাঘ)
- রেকর্ড নং চ-১১৬৩৮
- শিল্পী কে মল্লিক
- পর্যায় : গজল
- তাল : কাহাবা
- রাগ: পিলু বারোয়া (মিশ্র ইমন)
- প্রকাশকাল : ১৩৩৩, কল্লোল পত্রিকা-ফাল্গুন সংখ্যা ।
- গ্রন্থ : বুলবুল
প্রেক্ষাপট ও উৎস :
১৩৩৩ সালে কবি নজরুল কৃষ্ণনগরের চাপড়ির বিল নামক স্থানে হাঁস শিকার করতে গিয়েছিলেন। তখন ঠিক গোধূলী লগনে প্রকৃতির অকৃপন সৌন্দর্য এবং কবির নিজস্ব ভাবধারায় এ গজল গানটি তিনি রচনা করেছিলেন।
নজরুরের এ গান সম্পর্কে রাজেশ্বর মিত্র :
“বসিয়া বিজনে কেন একা মনে গানটির চরণ গজল অঙ্গের হলেও গানটির অবয়ব এবং বাণী-বিন্যাসে একটি ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়, যার সুর পিলু-বারোয়া বা মিশ্র ইমনে সজ্জিত।”
‘বসিয়া বিজনে’ গানটির পর্যায় বিশ্লেষণ :
নজরুল সৃষ্ট গতালের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে “বসিয়া বিজনে” গানটি মোটামুটি ভিন্ন আঙ্গিকের। গজলের মূল কথা প্রণয় বিষয়ক হলেও এই গানটিতে সান্ধ্যকালীন প্রকৃতির চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নজরুল সৃষ্ট গজলের মূল সুর এবং বাণীগত অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় উর্দু-ফার্সি গজলের আদলে রচিত। কিন্তু এই গানটি সম্পূর্ণ বাংলা কথায় এবং উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আদলে রচিত।

শব্দগত অবস্থান :
গানটির শব্দগত প্রত্রিয়া মোটামুটি স্বাভাবিক অঙ্গের বাংলা ভাষার সুন্দর শব্দ সংযোজন করেছেন তিনি এই গানটিতে। যার কারণে গানটির শাব্দিক নান্দনিক। অবস্থান পরিপূর্ণ।
ছন্দগত অবস্থান
গানের বাণী সব সময়ই ছন্দবদ্ধভাবে রচিত। অনেক ক্ষেত্রে কখনও কখনও এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। সুরের অবস্থান উপস্থাপনের জন্য গানে ছন্দবদ্ধভাবে শব্দ সংযোজিত হয়। সুরারোপিত বাণী গান হলেও তাল সংযোগে ছন্দময় শব্দ ও বাণী সমন্বয় সব ধরনের গানেই বিরাজমান।
‘বসিয়া বিজনে’ গানটিতে কাহারবা তাল ব্যবহার প্রসঙ্গ:
যে কোনো গানের দর্শনতাত্ত্বিক ভাবধারা গীতিকারের উপর নির্ভরশাল। সে ক্ষেত্রে সুর সংযোজন, তাল সংযোজন সবকিছুর সার্বিক উপস্থাপন ও মতামত তাঁর নিজস্ব। সে কারণে হয়তো-বা কবি নজরুল এ গানটিতে কাহারবা তাল সংযোজন করেছেন। কাহৱাবা তাল ৪/৪ ছন্দের যেহেতু, সেহেতু ৪/৪/৪/৪ ছন্দের ত্রিতাল, মধ্যমান, আদ্ধা-কাওয়ালী তালের ও বিন্যাস হয়তো করা যেত। কিন্তু গানের সুর বাণী, বাকা.. পর্যায় সবকিছু মিলিয়ে কাহারবা তালকেই সুন্দরভাবে কবি যুক্ত করেছেন। যাতে করে গানটি পরিপূর্ণতা পায়।
রাগের অবস্থান :
কাজী নজরুল তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সাধনের জন্যে প্রচলিত-অপ্রচলিত, মিশ্র প্রভৃতি রাগের সমন্বয় ঘটিয়েছেন এবং রচনা করেছিলেন অনেক রাগ ও তাল পিলু 1 রাগটি আরো অনেক পর্যায়ের গানে তিনি ব্যবহার করেছেন। এ গানটিতে তিনি পিলুর সাতে বারোয়া রাগের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যা পিলু-বারোয়া বা মিশ্র ইমন নামে পরিচিত। বলা হয় সবকিছুর বিশ্লেষণের আলোকে গানটির বাণীর সাথ রাগের নির্ভরতা সঠিক ছিল।

অবয়ব ও শেয়র
বাংলা গানের ধারায় লঘু সঙ্গীতের বিভিন্ন পর্যায়ের মতো “বসিয়া বিজনে” গানটিও একই অঙ্গের। প্রথমে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগের সমন্বয়ে অবয়ব রচিত হয়েছে। নজরুলের সৃষ্ট গজলে শেয়রের প্রাধান্য বা প্রভাব থাকলেও “বসিয়া বিজনে” গজলটিতে শেয়রের অবস্থান অনুপস্থিত।
অবয়ব বিশ্লেষণ :
স্থায়ী বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চলো লো গোরী।
চলো জলে চলো কাঁদে বনতল
ডাকে ছলছল জল-লহরি।।
বিশ্লেষণঃ
গানটির রচনা এবং সুরারোপে গোধূলী লগনের প্রকৃতির অকৃপন সৌন্দর্য শীলাকে বিন্যন্ত করা হয়েছে। এখানে নির্জন স্থানের একাকিত্বের যে অনুভব সেটা কোনো রমণীর কাল্পনিক অবস্থানকে কৰি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গানটিতে। গানটির স্থায়ী অংশে কোনো নারীকে উপমা প্রসঙ্গ হিসাবে উপস্থাপিত করে এই সন্দুর লগনে নদীজলে বা কোনো সরোবরে জল ভরণের কথা জানিয়ে কবি তাঁর অনুভব ব্যক্ত করেছেন। সাধারণত গ্রামীণ ধারাবাহিকতায় বধূদের মধ্যে দিনের শেষে অর্থ্যাৎ সন্ধ্যা শুরুর আগে প্রত্যেকের সীমাবদ্ধতায় এই বাণীর সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। নির্জন পরিবেশে কারো এই সুন্দর সময়টি বৃদ্ধা নষ্ট না করে কবি সার্বিকভাবে সবাইকে মোহিত করার জন্যে চেষ্টা করেছেন। যদিও দর্শনতাত্ত্বিক ভাবকবির নিজস্ব, তবুও মৌলিকত্ব এবং শাব্দিক চয়ন বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত ভাবধারাই ফুটে ওঠে।
অন্তরা
দিবা চলে যায় বলাকা পাখায়
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়।
কেঁদে চখাচখী মাগিছে বিদায়
বারোয়ার সুরে জুরে বাশরী ।।
বিশ্লেষণ :
গানটির প্রথম অন্তরায় জাগতিক ভাবধারার সাথে ঐশ্বরিক একটি তাত্ত্বিক রূপ সংযোজিত হয়েছে। “দিবা চলে যায় বলাকা পাখায়” কথাটি মানবিক অবস্থান এবং জীবনের একটি ক্লান্তিলগনের কথা বলা হয়েছে। মৌলিক জীবনের শেষে প্রত্যেকেরই জীবনাবসান ঘটে, সে প্রেক্ষাপটে মানব জীবনের অবসান যে সঠিক ও সার্থক হয় ঐশ্বরিক অবস্থানে এটাই অনুমেয়। জাগতিক প্রেম বিন্যাসের অবস্থানে বেলা শেষে বিহগের ঘরে ফেরার অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে।

সঞ্চারী
“বেলা গেল বধু” ডাকে ননদী
“চলো জল নিতে যাবি লো যদি”
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী
নাগরিকা সাজে সাজে নগরী ।।
বিশ্লেষণ
সঞ্চারী লঘু সঙ্গীতের তৃতীয় পর্যায়। এখানেও বাণীর দুটি অর্থবোধক অবস্থান লক্ষ্যণীয়। গ্রামীণ বধু ননদীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে নদীতে জল আনবার যে শব্দ চয়ন বা বাক্য বিন্যাসিত হয়েছে তার পুরোপুরি রূপটি কবি তাঁর গানটিতে তুলে ধরেছেন। সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তন হতে পারে। প্রকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় নদীতে আরোহণ করা সম্ভব নয় “কালো হয়ে আসে সুদৃঢ় নদী” গানটির বাণীতে তাই বোঝা যায়।
দ্বিতীয় অন্তরা
ওগো বে-দরদী ও রাঙা পায়ে মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে। তব সাথে কবি পড়িল দায়ে পায়ে রাখি তারে না গলে পরি।।
বিশ্লেষণে
দ্বিতীয় অন্তরার মূল বিষয়বস্তু মানবিক ভাবধারায় পৃথিবীর অবস্থানকেই বোঝানো হয়েছে। পৃথিবী ঘূর্ণয়মান অবস্থায় একটি মায়ার বাধন সব সময়ই মানব বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে রাখে। তাই কবি কণ্ঠে “ওগো বে-দরদী ও রাঙা পায়ে মালা হয়ে কেগো গেল জড়ায়ে” শব্দগুলো ধ্বনিত হয়েছে। জাগতিক যে নিয়ম গানটি স্পর্শ করেছে তাতে দুই ধরনের বস্তু সংক্ষেপই রচিত হতে পারে।
একটি ঐশ্বরিক প্রেম এবং অপরটি জাগতিক প্রেম। গানটি রচনার প্রেক্ষাপট ও রচনার স্থান উভয়ই গ্রামীণ মনোমুগ্ধকর পরিবেশের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতির গতি- প্রকৃতির ধারায় অনেক গানই রচনা করেছেন, কোথাও নদী সরোবরের কথা, কোথাও মাঝিমাল্লাদের মনের কথা, আবার কোথাও না জাগতিক প্রেমের কথা।

গীত- রীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এবং অবয়ব বিশ্লেষন করলে “বসিয়া বিজনে” গানটি কবির সুন্দর সময়ের রচনা বলা যায়। বিশ্লেষণ করবার পরিকল্পনা বা সারমর্ম লিখা অনেকের পক্ষে সম্ভব হলেও মূল ভাব দর্শন কবির নিজস্ব।