ঝুমুর গান ও কাজী নজরুল নিয়ে আজকের আলোচনা। রাঢ়বাংলার রুক্ষ মাটিতে নাচের ছন্দে চলে ঝুমুরের সুর ও তাল। মানুষ খোস্তা দিয়ে কোপায় শক্তমাটি, ছোট ছোট জঙ্গলে চলে তাদের শিকার।- এই মাটিকাটা ও শিকারের ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে ঝুমুর গান, চলে চাষের দ্রুত লয়ের সঙ্গে মাটি খোঁড়া, শিকার করা অথবা শক্তমাটিতে চাষ করার জীবিকার গতি ও ছন্দের সঙ্গ তাল মিলিয়ে যে সঙ্গীত, তা কখনোই নদী-বিধৌত অথবা পার্বত্য এলাকার সঙ্গীতের মত নয়।
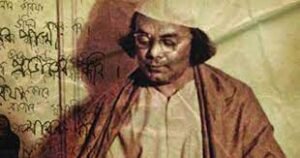
ঝুমুর গান ও কাজী নজরুল
ঝুমুরের মেপে চলা সুরের চলনে কাজী নজরুল ইসলাম সৃষ্ট ঝুমুর গানগুলি যথার্থ স্থান করে নিয়েছে। গানের ভাবে, ভাষায় ও সুরে কবির মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। ঝুমুর গান লোকসমাজে যেমন সাঁওতালী ঝুমুর ও বাংলা ঝুমুর- এই প্রেম- তার সঙ্গে কবি একাকার করেছেন রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে। আধ্যাত্মিক জগতের রাধাকৃষ্ণ নেমে এসেছেন রাঢ়বাংলার শক্ত মাটিতে।
প্রেমকথার মাঝে মাঝে কবি এঁকেছেন মানুষের বাস্তব জীবনের চিত্রকে। প্রেমিকা কখনো কয়লাখানের কামিন- তার মনের প্রেম জানাতেও কবি নিয়ে এসেছেন কৃষ্ণকথা- কৃষ্ণ কবির হাতে হয়েছেন কয়লাখাদেরই কোনো এক কুলি, যে সারাদিন ঘাম ঝরিয়ে দুমুঠো খাবার সংস্থান সহজে করে উঠতে পারে না।
এছাড়া এসেছে প্রকৃতির দৃশ্যপট, যা মানুষের মনে জাগায় মিলনের অনুভূতি। লোকজীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কবি তাঁর ঝুমুর গানে এনেছেন বেদের গান, তাদের জীবনকথা ও অলৌকিক বিশ্বাসের হাত ধরে কখনো কবি গেছেন তাদের প্রেমসাম্রাজ্যে, কখনো বা তাদের সাপখেলানোর চমকপ্রদ ভঙ্গীতে তিনি বর্ণনা করেছেন প্রাকৃতিক রূপ। যুক্ত হয়েছেন কৃষ্ণপ্রেমের কথাও।

কবি নজরুল ইসলাম সৃষ্ট বাংলা ঝুমুরে গৃহবধূ তার মনচোরার কথা মনে করতে করতে গৃহকর্মে হয় আনমনা,- তার পাস্তা ভাতে সে লবণের বদলে হলুদ দিয়ে ফেলে, গঞ্জনা সহ্য করে ঘরে বাইরে। প্রেমিক মানুষটির লাঙ্গল ও কাস্তে হাতে মাঠে 1 মাঠে তাকে খুঁজে পায় না, সুতরাং চোখের জলই তার সম্বল। কবি তাঁর প্রেমিকা গৃহবধূটির মুখে অসামান্য লৌকিক উপমার ব্যবহার করে গানটিকে একেবারে লোকজীনের নিজস্ব সম্পদ করে তুলেছেন।
‘তেল মেখে কি গায়ে তোরা/পীরিত করিস মনোচোৱা,
ধরিতে কি না ধরিতে যাস রে পিছলি’।
(‘ও দুখের বন্ধুরে, ছেড়ে কোথায় গেলি’)
সাঁওতালী ঝুমুরে এসেছে প্রেমকথা, তা একেবারে লৌকিক। যেখানে প্রিয় তার – প্রেমিকার মাথায় পরিয়ে দেয় ধুতুরা ফুল, যেখানে প্রিয়াকে সাজানো হয় বাবলা কুঁড়ির নাকছাবি, কুঁচের চুড়ি আর ঝুমকো দুল দিয়ে। এমন পাগল করা প্রিয়ের জন্যই তো সাঁওতালী মেঘের ঘরে ফেরাও হয় দায় (“কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো’)। মহুয়ার মদের নেশায় শুধু সাঁওতাল সমাজ বিভোর নয়, কবি প্রকৃতির বুকেও এেেছন সেই নেশার ঘোর।
মাতাল ছুঁড়ির নাচের তালে চাঁদও হয়ে উঠেছে বেসামসাল, এক মহুয়ার নেশায় বিভোর রাত্রিতে প্রকৃতি ও সাঁওতাল সমাজকে কবি করেছেন একাকার (‘চুড়ির তালে নুড়ির মালা রিনি ঝিনি বাজে লো’)। এমনই এক মাতাল করা বসন্তের দিনে ভ্রমরার যখন নিমফুলের মৌ পিয়ে ঝিম ধরে, তখন কবি আহ্বান জানিয়েছেন কুমুর নাচের (‘নিমফুলের ঝিম হয়েছে তোমরা’)। কখনো ঝুমরা নাচ নেচে যে সাঁওতাল কালো ছেলেটি আসে, তার আড় চোখের দৃষ্টিতে চাঁদও ‘আউরে’ যায় (“ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এল গো’)।

নাচের নেশার ঘোরে, মাদলের বোলে যখন কালো ছোঁড়া ছুঁড়িদের সঙ্গে ‘রাতের রাজা’ চাঁদও শালুকের কাঁকাল ধরে তালপুকুরের জলে হেলে দোলে নাচে, এমন মাতালকরা রাতেও কিন্তু বাঁশী শুনে মনের অবস্থা বোঝাতে ‘কয়লা খাদে ধোঁওয়ার কথা আনতে কবি ভোলেননি।
কারণ শুধু নাচের নেশার ঘোরেই এই মানুষগুলোর জীবন কাটে না,- এর পেছনে রয়েছে বাস্তব জগতের অনাহারক্লিষ্ট দিনগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ- আর কয়লাখাদের ধোঁওয়ায় চোখ জ্বলে যাওয়া (‘নাচের নেশায় ঘোর লেগেছে’)। নজরুল ইসলাম রচিত ‘শাল পিয়ালের বনে’ গীতিনাট্যের ঝুমুর গান আসন্ন বিরহের কথা ভেবে যে মানুষটির হৃদয় ব্যথায় ভরে ওঠে, যে ছেড়ে যেতে চায় না গিরিমাটির দেশ, তাই প্রকৃতির বুকে মিশে থাকার বাসনা, শুধু প্রিয়ার মুখ দেখার জন্য।
এমন এক রোমান্টিক ভাবনায় যখন কবি-সৃষ্ট মানুষটি বিভোর, তখনও – কয়লাধানের সর্বগ্রাসী ধোঁওয়ার কথা সে ভোলে না- এই ধোণ্ডা তাদের জীবনের অঙ্গ। তাই কালো মেঘে চাঁদ ঢেকে ফেলার বদলে কবি চাঁদকে ঢাকলেন কয়লাখাদের কালো ধোঁওয়ায়। গিরিমাটির দেশে শুদ্ধ রাড়বাংলার আদিবাসীদের একটা বড় অংশের জীবিকা হল শিকার, ভোজবাজি, সাপ খেলা দেখানো। ভাবিক কৰচ মাদুলি দিয়ে এরা মানুষের মনে বিশ্বাস অর্জন করে- অস্থায়ী এদের বাসস্থান।
“নিশিভোরের বেলা’ ‘বেদের নিঠুর ভীরের মত বাজে যার বঅশিত তার জন্য ভিনগায়ের কন্যার রাত কাটে নিদ্রাহীন, মন হয় আনমনা- গৃহকাজেও মন লাগে না। অস্থায়ী বেদের আকৰ্ষণীয়তাটা কৰি কাজে লাগিয়েছেন ঝুমুর গানের প্রেমকথায় (নিশি-ভোরের বেলা কাহার পাহাড়ী বাঁশি বাজে)। কন্যা কখনো বা সাপের চেহারায়, তখন সে ভয় পায় না বেদের ছেলের বাঁশিকে। সুযোগ পেলেই থাকতে পারে তার মনের ঝাঁপিতে (“বাঁকা ছবির মত বেঁকে উঠল যে তোর আঁখি রে’)। আবার বনের বেদেনীর অনেক ক্ষমতা- এমন লোকসমাজের বিশ্বাস।
আর এই বিশ্বাসে ভর করে কবি বেদেনীর কাছে চেয়েছেন তাঁর পছন্দমত প্রাকৃতকি সম্পদককে। এখানে বনের বেদেনী কবির হাতে হয়ে উঠেছেন প্রকৃতি দেব। তিনি একমাত্র পারেন আকাশের কোল থেকে চাদকে ধরে আনতে, ‘মেঘের ঝাঁপি খুলে ‘বিজরী সাপিনী’কে নাচাতে। আর সাগর ছ্যাঁচা পলার মালা পরে, বনের ঘাগরী পরে বেদেনী রূপিণী প্রকৃতিকে কবি আহবান জানয়েছেন তৃষ্ণা মেটাতে, যার আঁখির চাওয়ায় বিষ হারাবে কালনাগিনী (‘আয়লো বনের বেদিনী’)। বেদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে গানগুলো জড়িত।
কিন্তু নজরুল ইসলাম রচিত সাপুড়িয়ার গানে আমরা পেলাম এক অন্য বিষয়। তিনি মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে আরো বিস্তৃত পুরাণকথাকে যুক্ত করলেন। পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মনসার লোকপুরাণ বৃত্তকে কবি জড়িয়েছেন অভি যত্ন সহকারে। গানটিতে কৃষ্ণের বাঁশিই দেখাদিয়েছে সাপুড়ের বাঁশি হয়ে। বাঁশির শব্দে কালিদহে বহু সাপের আবির্ভাব। এবং সেই সাপের বিশে জর জর সখিদের অঙ্গ বাঁচাতে তারা আহ্বান করেছে বিষহরি কৃষ্ণকে।
যে চিত্রটি কবি গানটিতে এঁকেছেন তা একেবারেই লৌকিক কৃষ্ণ ও তাঁর বাঁশিতে শুনলাম না ব্রজের গুণ, শুধুমাত্র সাপুড়ের বাঁশির মতই তার কার্যকলাপ। সেই কারণে মনসাকে উপস্থিত হতে হল না। প্রয়োজন হলো বিষহরি কৃষ্ণকেই।
আরও দেখুনঃ

