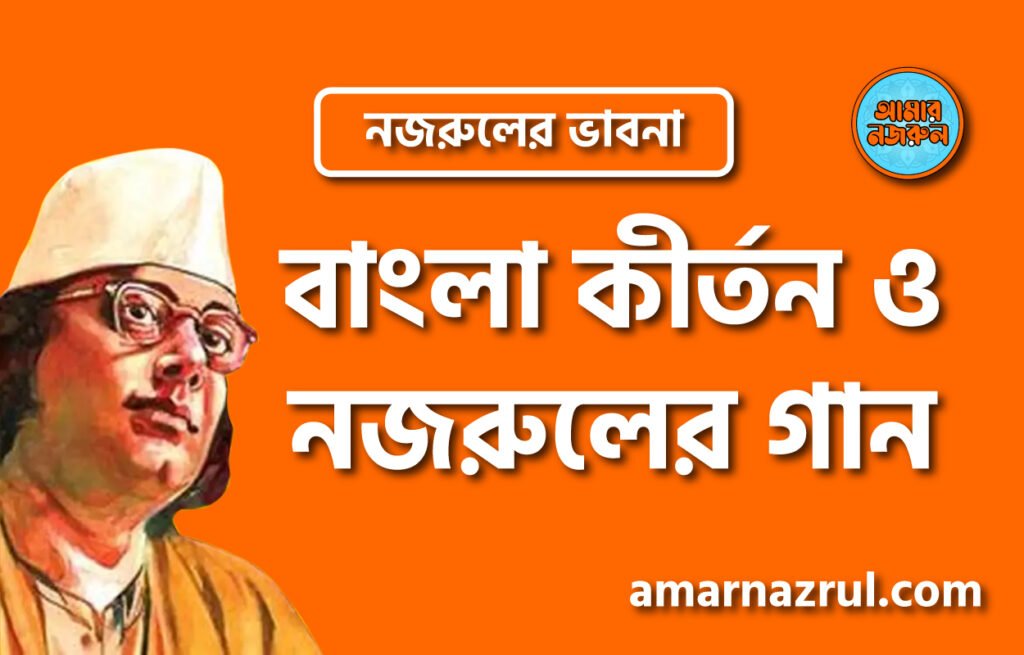বাংলা কীর্তন হলো কোন দেব-দেবীর নাম, গুণাবলী বা কীর্তিকাহিনী সম্বন্ধিত গান। প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম, কীর্তন গানের প্রকৃত উৎস।
বাংলা কীর্তন
কীর্তনের বৈশিষ্ট্য :
(১) “বহুগণভিমিলিত্বা” অর্থাৎ অনেকে একসঙ্গে মিলে এ আচরণটিই করে থাকেন।
(২) তদ্গান সুখম অর্থে আচরণের প্রথাগত নিয়মটি হলো গান করা। এই দুটি বৈশিষ্ট্য সমন্বয় করলে দেখা যায় অনেকে মিলে গান করে।
(৩) শুধু গান করলেই হবে না; গান সুখম অর্থাৎ সুখের নিমিত্ত। তদ্অর্থে ভগবানের অথবা ভগবদ ভক্তের। উক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করলে দেখা যায়, অনেকে মিলে ভগবত সুখের নিমিত্ত গান করে থাকে।
(৪) উচ্চৈভাষাতু অর্থাৎ শুধু গান করলে চলবে না। এই গান হবে উচ্চকণ্ঠের। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে রক্ষা করে যখন কীর্তন তার স্বরূপ নেয় তখন আরও অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য তাতে স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে।
এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:
(ক) এখানে “বহুগুণ” বলতে যারা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী বা যারা নিজস্ব সঙ্গীতে আস্থাশীল তারাই এই সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে থাকে।
(খ) এই গানে সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে কেবল খোল ও করতাল ব্যবহার করা হতো। তবে বর্তমানে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়।
(গ) এই গান একদিকে যেমন ঠাকুর মন্দিরের যা সমবেত কোনো মহলের আসরে গাওয়া হয়, অন্যদিকে আবার এই গান নগরের পথে পথেও গাওয়া হয়ে থাকে ।
(ঘ) কীর্তন গান যেহেতু ভববৎসুখের পরিবেশিত, সেহেতু যে পরিবেশে গান পরিবেশন করা হবে, সেই পরিবেশের পূর্ণ পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। ভগবৎ, বিগ্রহের ছবি, ফুলের মালা, তুলসীঘট, ধুপ-ধুনা ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
(ঙ) কীর্তনের বিষয়বস্তু হলো রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ এবং লীলার মধ্যে যে নাটকীয় সৌন্দর্য আছে তা ফুটিয়ে তোলাই হলো এ গানের মূল উদ্দেশ্যে। এই নাটকীয় ভাবকে অবলম্বন করে নানাবিধ রস ও রসপর্যায় সৃষ্টি হয়। সেগুলি বিন্যাস করা কীর্তন গানের উদ্দেশ্যে
(চ) কীর্তন গান মূলত গুরুমুখী। গুরু পরম্পরায় সে সাঙ্গীতিক ধারা, সুরতাল ইত্যাদি সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ক্রমপর্যায়ে গুরুপ্রদত্ত পদ্ধতিতে পরিবেশিত হয়।
(ছ) কীর্তনের বাচনিক অংশে দুটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে। একটি হলো উচ্চতর আদর্শময় উন্নত সাহিত্য, যেটি মূলত মহাজনদের রচনা। আর অপরটি হলো আবেগ প্রসূত লৌকিক এবং আঞ্চলিক ভাষামিশ্রিত ভাবের প্রকাশ, যেটিকে বলা হয় আখর বা গায়কের রচনা।
(জ) কীর্তন গানের ক্ষেত্রে শৈল্পিক নান্দনিকতার সমন্বয় লক্ষ করা হয় অর্থাৎ একাধারে ভক্তি অঙ্গের আর অন্যদিকে শিল্পের আচরণ।
(ঝ) কীর্তনের মধ্যে গতানুগতিকতা এবং আধুনিকতার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। গতানুগতিকতার ক্ষেত্রে কীর্তনের স্বরগত বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাগত মৌলিকতা রক্ষাই হলো মূল গতানুগতিকতা। আর আধুনিকতার ক্ষেত্রে বিন্যাসের নানা প্রকরণ শৈল্পিক ধারার নতুন সংস্কার সুরভাষা, গমক মীড় ইত্যাদির সংমিশ্রন। তা ছাড়া আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু যান্ত্রিক সংশ্লেষ ঘটেছে।
(ঞ) কীর্তন গানের ছন্দগত আস্বাদনের শেষ পর্যায়ে নৃত্যভঙ্গির প্রেরণা জাগে বিশেষত মাতন পর্যায়ে। এ নৃত্যে এষনা সৃষ্টি হয়। কবি জয়দেবকে পদ্ধাবতী চরণ চারণ কবি নামে ভূষিত করা হতো। এই বিশেষণ থেকে বোঝা যায় যে, জয়দেব ग গান করতেন পদ্ধাবতী তখন নৃত্য করতেন। সুতরাং নৃত্যে যে কীর্তনেরই আনুষঙ্গিক ক্রিয়া তা এ থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।
(ট) কীর্তনের গায়ক সর্বদাই ভক্তি অঙ্গের যাজক এবং সাধকদের মতো বেশ ধারণ করে থাকেন। কপালে তিলক, গায়ে উরণী চাদর, কণ্ঠে তুলসীর মালা, ফুলের মালা ইত্যাদি ধারণ করে একটি সাধনোচিত দৈহিক অবস্থা উপস্থান করেন।
(ঠ) কীর্তন গায়কের কণ্ঠ স্বাভাবিকভাবে উচ্চগ্রাম সম্পন্ন হওয়া দরকার। কণ্ঠের প্রকৃতি মীড়প্রধান এবং স্ফুরিত কম্পিত এবং উদারামক বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়াই উচিত।
(ড) কীর্তন গানের উপস্থাপন ক্ষেত্রে একটি নাটকীয়ভাব প্রয়োজন, কারন কীর্তন কেবল সুরের আস্বাদন নয়, এবং এর মধ্যে নাটকীয় বিচার বা বিষয়ের উন্মেষ ঘটানো হয় । কীর্তন কেবল অবসর সময়ের গান নয়, এটি হলো গ্রামীণ মানুষের সর্ববিধ আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কোনো কালপাত্র বা স্থানের বিচার নাই; অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই কীর্তনগান আস্বাদনীয়।
(ন) বাংলাদেশে সৃষ্টি হলেও কীর্তন উড়িষ্যা, মনিপুর, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে প্রসার লাভ করেছে। কীর্তন লোকসঙ্গীতের মতো স্বাভাবিকভাবে লোকচিত্ত হয়তো আকর্ষণ করে থাকে কিন্তু লোকসঙ্গীতের মতো সহজ সাবলীলতা কীর্তনে খুব বেশি নেই।
কীর্তনের ৫টি অঙ্গ:
কীর্তনে গানে সাধারণত ৫টি অঙ্গ থাকে ।
(১) কথা (২) দোঁহা (৩) আখর (৪) তুক্ ও (৫) ছুট।
কীর্তনের আরেকটি অঙ্গ- ঝুমুর। লোকায়াত ধারায় এই ঝুমুর অঙ্গের গানের প্রভাব আছে।
প্রহর প্রসঙ্গ:
বৈষ্ণবেরা মনে করেন যে, কলিযুগে ধর্ম নাম সংকীর্তন সার। এই সংকীর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রেম । হৃদয়ে এই প্রেম সঞ্চারনই বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান উপজীব্য। চৈতন্য দেব এই নামসংকীর্তনকে জনসঙ্গীতরূপে প্রবর্তন করেন। খোল ও কর্তালের সমন্বয়ে গীত হয় বলে কীর্তনের আরেক নাম সংকীর্তন। সংকীর্তন ও কীর্তন সমার্থক। উচ্চস্বরে হরিনাম করার নামই নামসংকীর্তন। এই নাম সংকীর্তন প্রহরব্যাপী, অষ্টপ্রহর এমন কি ২৪ প্রহর ব্যাপীও গীত হতে পারে।
কীর্তনে রাগের ব্যবহার:
বাংলাগানের বিবর্তনে চর্যাগীতি হতে মোটামুটি সকল পর্যায়ের গানে রাগের সংযুক্তি লক্ষ করা যায়। কীর্তন গানেও রাগের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: প্রভাতকালে ভৈরব-ভৈরবি, মধ্যাহ্নে বাগেশ্রী, সন্ধ্যায় পূরবী, ইমনকল্যাণ, রাতে-বেহাগ ইত্যাদি ।
কীর্তনে লীলাপ্রসঙ্গ:
শ্রী কৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করে যে সকল গীত রচিত তা লীলা কীর্তন নামে অভিহিত হয়। বাংলাদেশে যে লীলা কীর্তন প্রচলিত আছে তা মাত্র কয়েকটি লীলা অবলম্বনে রচিত যেগুলি প্রধানত বৃন্দাবনলীলা সম্পর্কিত। যেমন : জন্মলীলা, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, জল-ক্রীড়া, যুগল মিলন, বসন্তলীলা, হোলি লীলা, ঝুলন, কুঞ্জভঙ্গ, পূর্বরাগ, অভিসার, মান-বিরহ, বংশীশিক্ষা প্রভৃতি।
কীর্তনে রাস প্রসঙ্গ:
লীলা কীর্তনকে সঠিকভাবে রসকীর্তন নামে অভিহিত করা হয়। কীর্তনে ৬৪টি রস আছে। রস অর্থে যা আস্বাদন করা যায় অর্থাৎ যা চিন্তা করলে বা শুনলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়। আনন্দময় ঈশ্বরের লীলাও আনন্দের সৃষ্টি করে। এ কারণে লীলা কীর্তনের অপর নাম রসকীর্তন।
অবয়ৰ প্ৰসঙ্গ:
চর্যাপদের অবয়ব হিসাবেই কীর্তনের অবয়ব রচিত। যাকে বলা হয় উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। আধুনিক কালের সাঙ্গীতিক ভাষায় এই ৪টি বিভাগকে বলা হয় স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ।
কীর্তনে ব্যবহৃত তাল:
কীর্তনে ব্যবহৃত তালের সঙ্গে দক্ষিণী তালের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ধ্রুবতাল, শ্রুতিতাল রুদ্রতাল, বৃক্ষতাল, জপতাল প্রভৃতি।
কীর্তনে শাখা:
ষোল শতকের শেষ দিকে কীর্তন সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়েই কীর্তনেরমধ্যে কয়েকটি শাখা গড়ে উঠে। সেগুলো হলো, রেনেটি, মন্দারিণী, গরানহাটি, মনোহরশাহী ও ঝাড়খণ্ড। এই নামগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের নামানুসারে হয়েছে।
রেনেটি কীর্তন :
রেনেটি গানের জন্ম হিসাবে বলা যায় বর্ধমান জেলার দেবীপুর রাণীহাটি পরগনার বিপ্রদাস ঘোষ নামক কোনো এক প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ার সূত্রে এই গীতধারার সৃষ্টি হয়েছে। বহু খোঁজ করেও এই গানের বৈশিষ্ট্য বিশেষ পাওয়া সম্ভব হয়নি।
তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, গানগুলি হালকা ধরনের। কেবল তেওট তালের গানই এই ঘরানার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় রাধামোহন কর্মকার, কীর্তনীয়া মহাশয়ের মতে, “সুন্দরীঝটকর নটিনী সুবেশ” এই গানখানি রেনেটি তেওঁট। এছাড়াও আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রেনেটি তেওঁট গান হলো “মাধব মাকুরু মানিনীরাই, রেনেটি ঢং সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে গঠিত হয়। এর সুর, সরল ছয়ছয়ছন্দ ও গতি সংক্ষিপ্ত। এই ধারার গানের সাথে ঠুংরীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।
মন্দারিনী কীর্তন :
মন্দারিনী ধারা রেনেটি ধারা থেকেও সহজ, সরল সুরের প্রাধান্যযুক্তগান। শোনা যায় বংশীবাদন নামক কীর্তনীয়া এই ধারার প্রবর্তক। পাঁচালী বা মঙ্গল গানের অনুকরণে এই গান তৈরি। সঙ্গীত গবেষক হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই ঘরে তালের সংখ্যা মাত্র নয়টি।
মন্দারিনী গানের উৎসস্থল উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর সংলগ্ন বড় অঞ্চল। অনুমান করা হয় গড়মান্দারান বলে যে স্থানের বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থে চিহ্নিত হয়েছে অর্থাৎ যার বিবরণ বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে সেই সূত্রধরে মন্দারিনী গানের উৎপত্তি। মন্দারিনী গানেরও উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।
লোকমুখে প্রচলিত গানগুলিই হালকা সুরে ও তালে গাওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে মেদিনীপুর অঞ্চলের যে কীর্তনের সুর পাওয়া যায় সেগুলি মন্দারিনী ধারার সুর বলে অনুমিত হয়। এছাড়াও উড়িষ্যা, মেদেনীপুর অঞ্চলের সারিগানের মধ্যে মন্দারিনী ধারার অস্পষ্ট আদল খানিকটা পাওয়া যায়।
গড়ানহাটি কীর্তন:
পদকীর্তনের মধ্যে গড়ানহাটিই হলো আদি ও অকৃত্রিম। রাজশাহীর গড়ের হাট পরগনাতেই মূলত এই ধারা উৎপত্তি। আনুমানিক সপ্তদশ শতকের প্রথমে এই ধারার প্রবর্তন ঘটে। শ্রী চৈতন্যেদেবের জন্মের প্রায় শতাধিক বৎসর পর রাজশাহীর খেতুরী অঞ্চলের জমিদার কৃষ্ণনন্দ মহাশয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নরোত্তম দত্ত ঠাকুর ইনি জমিদারির কার্যভার থেকে মুক্তি নিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করে পরম বৈষ্ণব ভক্ত হিসাবে সর্বদা পরিচিত হন।
তখন তাঁর নাম হয় নরোত্তম দাস ঠাকুর। এই নরোত্তম ঠাকুর সমসাময়িক পদরচয়িতা গোবিন্দাদাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, গায়ক বানক দেবী দাস, গোরীদাস প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে যাজী গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য এবং নিত্যানন্দ ঘরণী শ্রীমতি কহবা দেবীকে সাক্ষী রেখে এই উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।
এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের হয় ধরনের বিগ্রহকে ছয়টি ভিন্ন নামে সংস্কার করা এবং ৬টি মন্দিরে এই বিগ্রহগুলি স্থাপন করা। এই উৎসবটি বাংলার বৈষ্ণব ইতিহাস প্রসিদ্ধ খেতুরী মহোৎসব বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এর উল্লেখ আছে নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে।
এখানে যে গীতবাদ্যের ধারা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হলো তা সর্বজন স্বীকৃত এবং সকলের জন্য আনন্দদায়ক। এই ধারাই হলো গড়ানহাটি কীর্তন ধারা।
গড়ানহাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে-সব তথ্যপাওয়া যায় সেগুলি হলো
(১) নানাবিধ তাল প্রয়োগে গানগুলি গাওয়া হয় ।
(২) গানগুলির বেশির ভাগই বিলম্বিত গতির।
(৩) গানের সুরে অনেকটা রাগের আভাস পাওয়া যায়।
(৪) গানে আখরের সংখ্যা কম।
(৫) কোনো ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত কথার প্রয়োগ নেই।
(৬) প্রত্যেকটি গানেরই পৃথক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এছাড়াও
গানগুলির চলনের মধ্যে প্রাচীন রাগরীতির লক্ষণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে ধ্রুপদের চলনের সাথে গড়ান হাটি কীর্তন ধারার মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। গরান হাটি ধারার মধ্যে লোকসঙ্গীত বা অন্যকোনো গানের প্রভাব তেমন দেখা যায় না।
তবে গড়ানহাটি ধারার গায়ন পদ্ধতি এত কঠিন ছিল যে, সাধারণের মধ্যে এই গানের প্রচার বা প্রসার বিশেষ ঘটতে পারেনি। তাই অভিজাত সঙ্গীতরীতি হিসাবে সমাদর লাভ করলেও খোলা আসরের পক্ষে তা উপযুক্ত ছিল না। তাই মানুষের কামা হয়ে উঠল সরল সহজ গায়ন পদ্ধতিতে উচ্চআদর্শযুক্ত অথচ দেশীয় রীতিপূর্ণ সর্বসাধারণের বোধগম্য এবং হৃদয়গাহী কোনো অলঙ্কারপূর্ণ গান। সেজন্যই গড়ানহাটি ধারার সরলকৃত রচনা বা গঠনশৈলী নিয়ে মনোহরশাহী ঢঙের উদ্ভব। তবে গড়ানহাটি ধারা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও কিছু বিশ্বস্ত গড়ানহাটি ঘরের গান যে একেবারে শোনা যায় না তা নয়।
যেমন: “মুঞি তো আগে জানুনা
হেই মা জানলে জলে যেতামনা
সেই কদম্বেরইতলে সখীরে”
মনোহারশাহী কীর্তন:
মনোহরশাহীগান কীর্তনের অতি জনপ্রিয় গান। এটি মূলত রাঢ় ভূমির গান। এর জন্মস্থান বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের সঙ্গমস্থল। অর্থাৎ কাটোয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল ও তার চতুর্দিকে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে। এই কীর্তন ধারা প্রাচীন এবং চৈতন্য সমসাময়িক বলে মনে করাই বিধেয়।
শ্রীখণ্ডের শ্রী নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। পূর্বসীলায় তিনি ছিলেন অধুনা। তাঁর যেমন ছিল সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা তেমনটি ছিল গাইবার ক্ষমতা। তিনি বাস করতেন শ্রীপাট শ্রীখণ্ড অঞ্চলে। ঐ গ্রামেরই ছিলেন রঘুনন্দন আচার্য। নিকটবর্তী অঞ্চলে ছিলেন প্রসিদ্ধ চৈতন্য মঙ্গল রচিয়তা, গায়ক ও কবি লোচনদাস।
ঐ গ্রামের অদূরে-ই বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জ্ঞানদাস। অদূরে নিকটবর্তী দাইহাটির সংলগ্ন অগ্রদীপে ছিলেন বাসুদেব ঘোষ। এঁরা সকলেই ছিলেন তখনকার দিনের দিকপাল গায়ক। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় ঐ অঞ্চলে পদাবলী কীর্তনের লীলা প্রকরণের উপযোগী একটি ধারা প্রবর্তিত হয়। এটিকে মনোহরশাহী ধারা বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধারার নামকরণ প্রশ্নে মতের পার্থক্য রয়েছে।
দেবীপদ ভট্টাচার্যের মৌখিক উক্তি মনোহরদাস নামক প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ার নাম অনুসারে এই ধারার নাম হচ্ছে মনোহরশাহী। কিন্তু এই মতের যৌক্তিকতা বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে, মনোহরদাস যদি একজন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াই হতেন তা হলে তাঁর রচিত বহুকীর্তনের পদ পাওয়া যেত। অপরমত হলো শ্রীখণ্ড বা সন্নিহিত অঞ্চলটিকে প্রাচীনকালে মনোহরশাহী পরগনা বলে ধরা হতো, সেই সূত্রেই ঐ অঞ্চলের গানের যে নতুন ধারা নতুন করে তৈরি হলো তাকে মনোহরশাহী ধারা বলে চিহ্নিত করা হয়।
ঐ ধারা প্রবর্তনের সময় নৃসিংহানন্দ, মিত্রঠাকুর, মঙ্গল ঠাকুর প্রমুখ তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক ছিলেন। এই গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন পদকে সংকলন করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা এবং মূল পদকে অক্ষুন্ন রেখে কিন্তু আঞ্চলিক কথা সহযোগে সুর তাল, ছন্দ যুক্ত করে একটি আকর্ষণীয় রূপসৃষ্টি করা অর্থাৎ মনোহরশাহী গানে গায়কের সংযোজনার সুযোগ অনেক বেশি।
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরস্পর গানগুলিকে অন্যসুরের আশ্রয় নিয়ে কিছু কিছু সংযোজন ঘটানো হয়। সেগুলিকে বলে ঘটকালি । তা ছাড়া গানগুলি প্রতি স্তরে মূর্ছন ও নৃত্যভঙ্গিতে ভরা থাকে। প্রকৃতপক্ষে রায়দেশীয় কীর্তনের মূল স্বরূপকে এই মনোহরশাহী গানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।
কেননা মূল পদগুলি গড়ানহাটি ধারার থেকেই গৃহীত। ফলে গানগুলির প্রথম স্তবকের প্রথম চরম গড়ানহাটির মতোই বিলম্বিত হয়ে নানাবিধ বড় তালে গাওয়া হয়ে থাকে। তারপরই সুরের মধ্যে একটা হালকা ধরন আসে এবং তাল ফেরতাযুক্ত হয়। আঞ্চলিক প্রভাব মনোহরশাহী গানে সবচেয়ে বেশি।
যেমন
(১) কওহে গোপী কিসের লাগি বল কেন আস (রামলীলা প্রসঙ্গের গান)
(২) বিষম বাশীর কথা কহনে না যায় (বংশী প্রসঙ্গে রাগ)
ঝাড়খণ্ডী কীর্তন:
বাংলার কীর্তন বিভিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে বিকশিত হয়েছিল। তবুও একথা সত্যি তার প্রতিটি বিকাশের ইতিহাস আজও স্পষ্ট নয়। আঞ্চলিক অন্বেষণের সূত্রে প্রবীণ গবেষকদের মতানুসারে এবং উল্লেখ্য গ্রস্থানির বিচার বিশ্লেষণে করে ঝাড়খণ্ডী ধারার কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধারাকে ভালো করে দেখলে লোকসঙ্গীতের সাথে এর একটা সামঞ্জস্যের আভাস পাওয়া যায়।
ঝাড়খণ্ড স্থানটি হলো বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকণ্ঠে অর্থাৎ পুরুলিয়া জেলার প্রান্ত অঞ্চল, মানভূম হয়ে উড়িষ্যা যাবার পথে। চৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্য ভাগবতে এই ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে মনে হয় অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। জনবসতি ছিল কম। পথটি যদিও দূর্গম তবুও ঐ পথ দিয়েই ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে পায়ে হেঁটে উড়িষ্যা যাওয়া হতো।
স্বয়ং মহাপ্রভুও পায়ে হেঁটে ঐ পথেই ঝাড়খণ্ড অর্থাৎ মানভূম, ছোটনাগপুর হয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। কারণ মহাপ্রভুর এই পরিক্রমা ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের সামন্তরাজা, জমিদার তথা আদিবাসীদের উপর এক অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। ফলে রাজা, জমিদার, প্রজা অনেকেই বৈষ্ণবধর্ম অনুরাগী হয়ে পড়েন, এমনকি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে সঙ্গীত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব প্রচণ্ডভাবে পড়ে। আঞ্চলিক সঙ্গীত ধারা মহাপ্রভুর কীর্তনধারায় প্রভাবিত হয়ে ওঠে। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে এইভাবেই প্রথম কীর্তনের সূত্রপাত।
এই সূত্র থেকেই পরবর্তী কালে ঐ অঞ্চলের লোকদের প্রচেষ্টায় রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক উচ্চাঙ্গ পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে মানভূমের আঞ্চলিক সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ঝাড়খণ্ডী কীর্তন গানের প্রবর্তন হয়। মানভূমের আঞ্চলিক সুর বলতে এখানে ঝুমুরকেই বোঝানো হয়েছে।
শোনা যায় শ্রী নিবাস আচার্যের শিষ্য গোকুল নন্দ সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বা সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে এই নতুন কীর্তন ধারার জন্মদান করেন। গোকুলনন্দ ছাড়া অন্যকোনো প্রবর্তকের নাম ঝাড়খণ্ডী কীর্তন ধারার ক্ষেত্রে তেমন সুষ্পষ্ঠভাবে পাওয়া যায় না।
তবে চৈতন্যউত্তর যুগে ঐ অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বৈষ্ণবীয় আচরণের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। ফলে বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির সংঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির একটা আদন-প্রদান ঘটে। ফলে আদিবাসী ঝুমুর গানের সঙ্গে ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তনের মিলিত ফলস্বরূপ ঝাড়খণ্ডী ধারার আত্মপ্রকাশ ঘটে।
ঢপকীৰ্ত্তন কীর্তন :
বাংলাদেশে প্রচলিত এ ধরনের কীর্তনাঙ্গের গান অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই গান হলো ঢপগান বা ঢপকীর্তন। এ গান পদাবলী কীর্তনধারা হতে জন্ম নিলেও মূল ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। লৌকিক কীর্তন ধারারূপে পদাবলী কীর্তনের পাশাপাশি এই ধারা চলতে আ করে এবং ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ভিন্ন পথে চালিত হয় এবং পথ হারায়।
বলা যায় কীর্তন গান লৌকিক স্তরে নেমে এসে যেরূপ লাভ করে ঢপ কীর্তন তাদেরই অন্যতম। ঢপ নাম করণের কারণ হলো প্রথাগত কীর্তনের সঙ্গে কিছু সহজ সরল এবং চটুলসুরের সংযোজন করে নতুন হালকা ধরনের গান পরিবেশন করা। কীর্তন ভেঙে মূলত বাংলায় ঢপকীৰ্ত্তন সৃষ্টি হয়। মুর্শিদাবাদের রূপচান অধিকারী ( ১৭২২ খ্রিঃ-১৭৯২, ১১২৯-১১৯৯ বঙ্গাব্দ) ও বনগ্রামের মধুসূদন (যশোহর জেলা) (১৮১৮- ১৮৬৮ খ্রিঃ, ১২২৫-১২৭৫ বঙ্গাব্দ) বা মধুকানের প্রয়াসে এই কীর্তনের উদ্ভব।
মনোহরশাহী কীর্তনের সুরভেঙে সহগ্রাহ্য সুরে তালে রচিত চপকীৰ্ত্তন একসময় বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। আখরবিহীন এই ঢপে পাঁচালী ও যাত্রাগানের প্রভাব সুস্পষ্ট। ঢপ কীর্তনের শিক্ষাগুরু ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। অবশ্য হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতানুসারে গানের সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুকাননের নাম সর্বাগ্রে করা উচিত।
কিন্তু এ সিদ্ধান্তের গবেষণামূলক কোনো বিচার হয়নি। কারণ সমসাময়িক কীর্তন গানগুলিতে চটুল প্রকৃতির যে চণ্ডীদাসের সুর অর্থাৎ লোক তালের “পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া” গানের সুরের মতো সুর সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। মধুকান যদি সেই সুরের অনুকরণে ঢপকীর্তনের সুর তৈরিও করেন তবে তাকে সৃষ্টি না অনুকরণই বিধেয়। সেটা যাই হোক “ঢ” নামটি কিন্তু মধুকানেরই দেয়া। মধুকান রাধামোহন ঠাকুরের সুযোগ্য ছিলেন এবং প্রচুর চপকীর্তন তিনি রচনা করেন।
অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ঢপকীর্তন মধ্যবাংলায় বেশ ভালোমতো প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ঢপকীর্তন গাওয়ার বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি ছিল। এ গানে মূল গায়েন থাকতেন একজন এবং বাকি যারা থাকতেন তারা ছিলেন ধুয়াধারী বা দোহার। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে এই গান করতেন। দলের অধিকারীরা নিজেরাই গান বাঁধতেন।
বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর প্রভাবে এবং ভাঙা কীর্তনের সুরে ঢপের গানগুলি তৈরি হলেও কীর্তনের মূল নীতিকে এগানের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হতো না। ঢপকীর্তনে সধারণত তিন/ চার/ পাঁচ সাত ও ১০ মাত্রার তাল ব্যবহৃত হয়। উচ্চাঙ্গ কীর্তনের মত দশকোষী, আড়, লোফা প্রভৃতি জটিল তালের ব্যবহার নেই। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হারমোনিয়াম, বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, করতাল প্রভৃতি একসাথে বেজে ওঠে ।
সময়ে সময়ে, আসর জমানোর জন্য নৃত্যও সংযোজিত হয়। পূজা-পার্বন যেকোনো অনুষ্ঠানে, ঝুলন, দোলযাত্রা, জন্মষ্টমী প্রভৃতি যে-কোনো ধর্মীয় উৎসবে আখড়ায় বা নাটমন্দিরে ঢপগানের আসর বসানো হতো। বিশ্বকোষ থেকে জানা যায় যে বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত গোপাল নগর নিবাসী মহোনদাস বৈরাগী ঢপকীর্তনের নতুন পদ্ধতির সৃষ্টি করেন।
ঢপগানের জগতে কিছু মহিলা শিল্পীরও আত্মপ্রকাশ ঘটে। এদের মধ্যে পান্নাবাঈ, পটলবাঈ, ছাপান্ন ছুরী, কমলা ঝরিয়া, ললিতা বৈষ্ণবী প্রমুখেরা যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন। পুরষ গায়কের মধ্যে লোচন দাস বা দ্বারিকদাস, আঘোর দাস, শ্যামবাউল, শ্রীদাম দাস, নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথী রায় কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখের নাম প্রসিদ্ধ।
উপরোক্ত আলোচনায় আমরা এই বাক্য সমন্বয় ঘটাতে পারি যে, বাংলাগানের বিবর্তন প্রশ্নে ঢপকীর্তন গান সাঙ্গীতিক ধারার ব্যাপ্তি বিষয়ক একটি উপখ্যান, যাতে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ ছাড়াও রামায়ণ এবং মহাভারতের বিবিধ প্রসঙ্গ।
নজরুলের কতিপয় কীর্তন গান উল্যেখ করা হলঃ
১) আমি কলহের তরে কলহ করেছি
২) আমি কেন হেরিলাম নবঘনশ্যাম
৩) একি অপরূপ রূপের কুমার
৪) ওগো প্রিয় তুমি চলে গেছ আজ
৫) ওলো বিশাখা ওলো ললিতে এই পথের ধুলী দে
৬) কেমনে রাধার কাঁদিয়া বরষ যায়
৭) তোরা যা লো সখি মথুরাতে
৮) নওল শ্যামতনু গোরীর পরশে
৯) না মিটিতে মনোসাধ
১০) নাটুয়া ঠমকে যায়
১১) বাজে মঞ্জুল মঞ্জীর রিনিকি ঝিনি
১২) ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই
১৩) ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে
১৪) ফুটিল মানশ মাধবী কুঞ্জে
১৫) মোরে সেই রূপে দেখা দাও
১৬) ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা
১৭) মনিমঞ্জীর বাজে অরুণিত চরণে
১৮) মুরলী শিখব বলে
১৯) মোর মাধবশূণ্য মাধবীকুঞ্জে
২০) যা সখি যা তোরা গকুলে ফিরে
২১) শ্যমমুখ আর না হেরব
২২) সখি আমিই নাহয় মান করেছিনু
২৩) সখি সাজায়ে রাখলো পুষ্পবাসর
২৪) সখি সেই তো পুষ্পশোভিতা হলে
২৫) সখি যায় নি তো শ্যাম মথুরায়, প্রভৃতি।
আরও দেখুনঃ